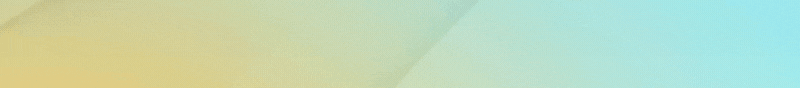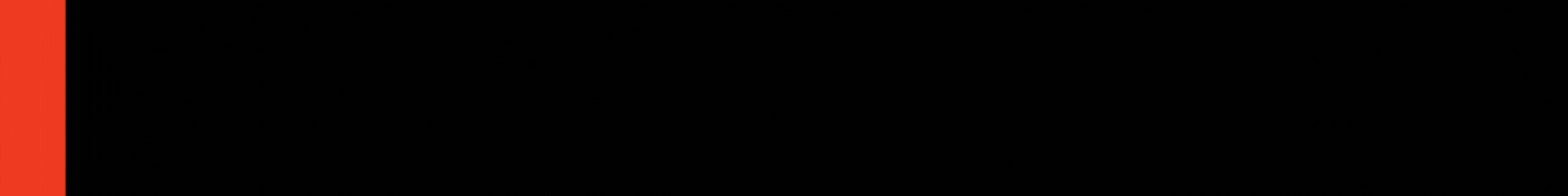লবণাক্ততায় ৩০ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন বঞ্চিত উপকূলীয় অঞ্চল
- প্রকাশিত: রবিবার, ২ নভেম্বর, ২০২৫
- ৯৭ বার পড়া হয়েছে

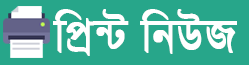
বিশেষ প্রতিনিধি : জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে লবণাক্ততার মাত্রা বাড়ছে উপকূলীয় অঞ্চলের জমিগুলোয়। ছড়াচ্ছেও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। লবণাক্ততার তীব্রতায় আবাদি জমি হয়ে পড়ছে অনাবাদি। ফলন কমছে, শস্যের গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ক্ষত। মৃত্তিকা সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (এসআরডিআই) এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে, শুধু লবণাক্ততার কারণেই প্রতি বছর উপকূলীয় জেলাগুলো খাদ্যশস্য উৎপাদন-বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে ৩০ লাখ টনের বেশি।
উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষিতে লবণাক্ততার প্রভাব নিরূপণে সম্প্রতি গবেষণাটি চালায় এসআরডিআই। এতে উঠে এসেছে, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তাসহ সার্বিক আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতেই বড় মাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে লবণাক্ততা। এ লবণাক্ততা বাড়তে থাকায় উপকূলীয় অঞ্চলের মাটিতে অণুজীবের সক্রিয়তা কমে যাচ্ছে। একই সঙ্গে মাটিতে জৈব পদার্থ, নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের সহজলভ্যতাও কমে যাচ্ছে। এর বিপরীতে বাড়ছে কপার ও জিংকের মাত্রা। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের কারণে লবণাক্ততা কিছুটা হ্রাস পায়। ওই সময় কিছু লবণাক্ত এলাকায় ধানের, বিশেষ করে আমন ফসলের আবাদ করা সম্ভব হয়। তবে মৌসুমের শেষ দিকে বৃষ্টি কমায় ফসলে দানার সংখ্যাও হ্রাস পায়। এতে করে ফলন ঠিকমতো পান না কৃষক। লবণাক্ততার প্রভাবে মাটির উর্বরতা যেমন কমছে, তেমনি কমছে গাছের উৎপাদনক্ষমতাও।
এসআরডিআইয়ের হিসাব অনুযায়ী, উপকূলীয় অঞ্চলে মাঝারি থেকে খুবই তীব্র মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ৮ লাখ ৭০ হাজার হেক্টর (স্বল্পমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত জমিকে বাদ দিয়ে)। এসব জমিতে প্রতি বছর লবণাক্ততার কারণে শস্য উৎপাদন কম হচ্ছে হেক্টরপ্রতি গড়ে ৩ দশমিক ৪৮ টন করে। সব মিলিয়ে উপকূলীয় অঞ্চলের জমিগুলো শুধু লবণাক্ততার কারণে ফলন হারাচ্ছে ৩০ লাখ ২৭ হাজার টনেরও বেশি। প্রতি কেজি শস্যের গড় মূল্য ৭৭ সেন্ট হিসেবে বছরে এ ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩৬ কোটি ৭১ লাখ ২০ হাজার ডলারে, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ৩ হাজার ১২০ কোটি টাকা (১ ডলার সমান ৮৫ টাকা)। অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত জমির পুষ্টি প্রতিস্থাপনে ব্যয় হচ্ছে ১ কোটি ৩৫ লাখ ৬০ হাজার ডলার করে, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ১১৫ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে দেশে প্রতি বছর শুধু উপকূলীয় জমিতে লবণাক্ততার কারণে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে ৩ হাজার ২৩৫ কোটি টাকা করে।
স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালেও উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত জমির পরিমাণ ছিল ৮ লাখ ৩৩ হাজার হেক্টর। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ লাখ ৬০ হাজার হেক্টরে। সে হিসেবে গত চার যুগে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত জমির পরিমাণ বেড়েছে ২৭ শতাংশের বেশি। এর মধ্যে হালকা মাত্রায় লবণাক্ত জমির পরিমাণ ১ লাখ ৯০ হাজার হেক্টর, মধ্যম মাত্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার, তীব্র মাত্রায় ৪ লাখ ২০ হাজার ও খুব তীব্র মাত্রায় লবণাক্ত জমির পরিমাণ ২ লাখ হেক্টর। উপকূলীয় অঞ্চলে এসব এলাকায় মোট আবাদি জমির পরিমাণ ২৮ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে চাষযোগ্য ২১ লাখ ৬২ হাজার হেক্টর। সে হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চলের চাষযোগ্য জমির প্রায় অর্ধেকই লবণাক্ত। লবণ পানির ভয়াবহতার কারণে প্রতি বছর শুষ্ক মৌসুমে উপকূলীয় এলাকায় পাঁচ লাখ হেক্টরের বেশি জমি অনাবাদি থেকে যায়।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কারণেই উপকূলীয় অঞ্চলের মাটিতে সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটছে। একই সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানিতেও লবণাক্ততা বাড়ছে। এছাড়া জলোচ্ছ্বাসের সময়েও সমুদ্রের নোনাপানি উঁচু ভূমিতে উঠে আসে। পরে তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেয়া হয় না। নদীতে সুপেয় পানির অভাব থাকায় নোনাপানি অপসারণ প্রক্রিয়াটিও বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাব, উপকূলীয় নদ-নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় জোয়ারের সময় বাঁধ উপচে পড়ছে। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি চলে আসছে কৃষিজমিতে। ব্যাহত হচ্ছে কৃষিজমির স্বাভাবিক উৎপাদনক্ষমতা।
এ বিষয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত বলেন, এ অঞ্চলের নদীর পানি ক্রমান্বয়ে লবণাক্ত হয়ে পড়ছে। লবণাক্ততার কারণে পরিস্থিতি গুরুতর খারাপের দিকেই যাচ্ছে। লবণাক্ত পানি প্রবেশ ঠেকাতে না পারা ও দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের কারণে বিপর্যয় আরো বাড়বে। জমি আবাদযোগ্য করে তুলতে না পারলে তার প্রভাব পড়বে জনজীবন ও বাস্তুসংস্থানে। লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন ও তা দ্রুত কৃষকের কাছে পৌঁছানো এবং উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করতে হবে। এছাড়া এ অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করে লবণ পানি প্রবেশ ঠেকাতে হবে। সার্বিকভাবে এ অঞ্চলের উন্নয়নে সমন্বিত পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন জরুরি।
কৃষিমন্ত্রীর নেতৃত্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের এক বিশেষজ্ঞ টিম সম্প্রতি খুলনার উপকূলীয় অঞ্চলে পরিদর্শনে যান। এ পরিদর্শন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল কৃষির উন্নয়ন ও সম্ভাবনা এবং প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় কর্মকৌশল নির্ধারণ। ওই সময় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেন, দেশের উপকূলীয় ও দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে কৃষি উৎপাদনের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে ধান, ডাল, তরমুজ, আলু, ভুট্টা, বার্লি, সূর্যমুখী, শাকসবজিসহ অনেক ফসলের লবণাক্ততাসহিষ্ণু উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। এসব জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উপকূলবর্তী বিপুল এলাকার চাষীদের মধ্যে দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য কাজ চলছে। এ লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে। চাষীরা এসব ফসলের চাষ করলে দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় নতুন করে কৃষি বিপ্লব ঘটবে। আমন ধান তোলার পর বছরের বাকি সময়টা মাঠের পর মাঠ জমি অলস পড়ে থাকত। এ প্রতিকূল ও বিরূপ পরিবেশে বছরে কীভাবে দুবার বা তিনবার ফসল চাষ করা যায়, সে লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি।
গবেষণায় বলা হয়েছে, উপকূলীয় অঞ্চলের জমিগুলোয় আবাদের ক্ষেত্রে চার ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। এ চার ধরনের পদ্ধতিতে সিংহভাগ সময়ই জমি পতিত থাকে। এর মধ্যে পতিত-পতিত-রোপা আমনে ব্যবহূত হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চলের ৩৮ দশমিক ৫ শতাংশ জমি। ফলে এখানে দুই মৌসুমেই পুরো জমি পতিত থাকছে। অন্যদিকে রবি-আউশ-রোপা আমনে ব্যবহূত হচ্ছে ২৪ শতাংশ জমি, পতিত-রোপা আউশ-রোপা আমনে ব্যবহূত হচ্ছে ১৪ দশমিক ১ শতাংশ জমি এবং পতিত-বোরো-রোপা আমনে ব্যবহূত হচ্ছে ৯ দশমিক ৬ শতাংশ জমি। অতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে এ অঞ্চলের অধিকাংশ জমি পতিত থাকছে। এ কারণে এ অঞ্চলে লবণক্ততাসহিষ্ণু ধানের ও শস্যের জাত সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে ধান, সবজি, মসলাজাতীয়, ফল ও তেলজাতীয় শস্যের আবাদ বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে এখানে। পাশাপাশি মাটি ও পানি ব্যবস্থাপনায় জোরদারের মাধ্যমে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করার বিষয়টিও জরুরি হয়ে পড়েছে।
বিশ্বব্যাংকের ‘রিভার স্যালাইনিটি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এভিডেন্স ফ্রম কোস্টাল বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক গবেষণার তথ্যমতে, ২০৫০ সালের মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৪৮টি থানার মধ্যে ১০টি থানার বিভিন্ন নদীর পানি মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততায় আক্রান্ত হবে। এগুলো হলো সাতক্ষীরার শ্যামনগর, আশাশুনি, কালিগঞ্জ, খুলনার বটিয়াঘাটা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, কয়রা, পাইকগাছা, বাগেরহাটের মোংলা ও পটুয়াখালীর কলাপাড়া। বর্তমানে এখানে ১০ পিপিটি মাত্রার কাছাকাছি লবণাক্ততা বিরাজ করলেও ২০৫০ সালের মধ্যে তা কোনো কোনো স্থানে ২৫ পিপিটি মাত্রায় উন্নীত হবে। ওই সময়ে লবণাক্ততা, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য জলবায়ুসংক্রান্ত বৈরী প্রভাবের কারণে বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ৩৩ লাখ উপকূলীয় মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে। এছাড়া উপকূলীয় তিন জেলা খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরার ১ হাজার ৬৫০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধের অবস্থা এখন বেশ নাজুক। প্রায় ৬০ বছর আগে তৈরি এসব বাঁধের এখন আর দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা নেই। এ কারণে উপকূলীয় অঞ্চলজুড়ে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে নোনাপানি। আবাদহীন হয়ে পড়ছেন স্থানীয়রা। কাজ হারিয়ে অন্য জেলায় উদ্বাস্তু হচ্ছে উপকূলের মানুষ।
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যারা দায়ী, তারা এ জন্য ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে না। তাই বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হচ্ছে। জলবায়ু ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণে বাংলাদেশের গৃহীত কর্মপরিকল্পনার সুফল পাচ্ছে দেশের মানুষ। আবার বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে ইতিমধ্যে জলবায়ু ঝুঁকি নিরসনে বাংলাদেশ বিশ্বের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মূলত বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বাতাসে কার্বন নিঃসরণ বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে, বাড়ছে বরফ আচ্ছাদিত অঞ্চলের বরফ গলার পরিমাণ। এতে বাড়ছে সমুদ্র পৃষ্টের উচ্চতা, বাড়ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিও।
পরিণামে বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে পরিবেশ-প্রকৃতিকে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশ মোটেও দায়ী নয়। বরং তুলনামূলক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা জার্মান ওয়াচে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। এ ছাড়াও ব্রিটিশ গবেষণা সংস্থা ম্যাপলক্র্যাফটের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ ১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।
দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যারা দায়ী তারা এ জন্য ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে না। তাই বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হচ্ছে। জলবায়ু ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণে বাংলাদেশের গৃহীত কর্মপরিকল্পনার সুফল পাচ্ছে দেশের মানুষ। আবার বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে ইতিমধ্যে জলবায়ু ঝুঁকি নিরসনে বাংলাদেশ বিশ্বের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।
বাংলাদেশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মূলত বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে। এতে সমুদ্র পৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমাগত। অন্যদিকে অ্যান্টার্কটিকাসহ হিমালয়ের বরফ গলা জলের প্রবাহে সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক বন্যাসহ নদ-নদীর দিক পরিবর্তন। এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে নদ-নদীর ভাঙন। পাশাপাশি সমুদ্রের পানিতে বাড়ছে লবণাক্ততাও। এতে দেশের সমুদ্র উপকূলের মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে লবণাক্ত পানি পানে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। নারীরা সন্তান ধারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। এ ছাড়াও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে দেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে গ্রীষ্ম মৌসুমে মরুকরণের সৃষ্টি হচ্ছে। এ বিষয়ে বিশ্বখ্যাত মরুভূমি গবেষকরা বাংলাদেশকে সতর্কও করে আসছেন বারবার। দেশের এ সমস্যাগুলোকে বাংলাদেশ ‘ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান’ দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।
শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ছাড়াও ঋতুভেদে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, নদীভাঙন, ভূমিধস প্রভৃতি মিলিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বলা হয় বাংলাদেশকে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের ঋতুচক্রের হেরফেরের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগেরও হেরফের ঘটছে। অর্থাৎ আগের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সেই স্বাভাবিক চিত্র এখন আর আমাদের নজরে পড়ে না। এর প্রধান কারণ তাপমাত্রার পরিবর্তন বা বৈশি^ক উষ্ণতা বৃদ্ধি। এর প্রভাবে বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, সমুদ্রস্তরের উচ্চতা, মরুকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে, পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের চিরচেনা ষড়ঋতুতে। সাহিত্যে বাংলাদেশকে ষড়ঋতুর দেশ বা বছরে ছয় ঋতুর বর্ণনা থাকলেও বাস্তব অর্থে এখন ষড়ঋতু পরিলক্ষিত হয় না। বৃষ্টির সময়ে বৃষ্টি কম বা না হয়ে অন্য সময় হচ্ছে, বম অথবা অতিবৃষ্টি, বন্যা হচ্ছে। অন্যদিকে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় নদ-নদীর পানি প্রবাহ শুকিয়ে যাচ্ছে। নদীর গতিপথ পরির্বতন হচ্ছে, নদী ভাঙছে। অন্যদিকে নদীর পানির বিশাল চাপ না থাকায় সমুদ্রের লোনাপানি যতটুকু এলাকাজুড়ে আটকে থাকার কথা ততটুকু জায়গায় থাকছে না। পানির প্রবাহ কম থাকার কারণে সমুদ্রের লোনাপানি স্থলভাগের কাছাকাছি চলে আসছে।
ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের বিপুল এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে ত্রমাগত।
বিশেষজ্ঞদের অভিমত হচ্ছে, বাংলাদেশে কম বৃষ্টিপাতের কারণে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার সমস্যা দিন দিন আরও প্রকট হয়ে উঠছে। এদিকে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ও লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় সুন্দরবনের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। বিশেষ করে বাইন ও সুন্দরী গাছসহ বিভিন্ন গাছের আগামরা রোগ দেখা দিয়েছে। তাতে আবার নানা ধরনের পাতা ও ফুলখেকো বিভিন্ন রকমের কীটের আবির্ভাবও ঘটেছে। এ ব্যাপারে জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের অভিমত, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে ইকোসিস্টেমের বিষয়টি সরাসরি জড়িত। তাই দেশের কোনো অঞ্চলের জলবায়ুর পরিবর্তন হলে সে অঞ্চলের প্রাণিকুল অথবা কীটপতঙ্গের জীবনধারায়ও পরিবর্তন আসে, প্রাণীর অস্তিত্বও সংকটে পড়ে। এমনও হয় যে, সেসব অঞ্চলের প্রাণিকুলের বিলুপ্তি ঘটে নতুন প্রাণিকুলের সৃষ্টি হয়। মূলত এভাবেই ওই অঞ্চলের জলবায়ুর প্রভাবে বিভিন্ন প্রজাতির কীটের আবির্ভাব ও পূর্বের প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে।
দেশীয় প্রজাতির গাছগাছালি হারিয়ে যাওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে বিদেশি গাছের আগ্রাসন। বিদেশি এসব গাছ ও লতাগুল্মের ক্রমাগত বর্ধনের ফলে গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের প্রকৃতি থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেছে প্রায় এক হাজার প্রজাতির নিজস্ব গাছ। উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে, বিদেশি আগ্রাসী গাছগুলো এখন আমাদের দেশীয় প্রজাতির গাছ হিসেবে শনাক্ত হচ্ছে। যেমন-সেগুন, মেহগনি, আকাশমণি, রেইনট্রি, বাবলা, চাম্বল, শিশু, খয়ের ও ইউক্যালিপ্টাস গাছ এখন অনেকের কাছে দেশীয় প্রজাতির গাছ হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। অথচ এগুলো ভিনদেশি গাছ। এসব গাছের কারণে দেশীয় প্রজাতির গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ প্রজাতির গাছগুলোর জন্য অনেক জায়গার দরকার হয়। এগুলো দেশি গাছের তুলনায় অনেক দ্রুত মাটি থেকে বেশি পরিমাণে পুষ্টি শুষে নেয়। এ ছাড়াও আশপাশে দেশীয় প্রজাতির গাছের বেড়ে ওঠাকে ব্যাহত করে। মূলত এ গাছগুলো ব্রিটিশ আমলে এতদঞ্চলে বিভিন্নভাবে আনা হয়েছে।
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের কৃষিতে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এর ফলে কৃষিকে নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। একই সঙ্গে এতে বিরূপ প্রভাব পড়ছে কৃষি, চাষাবাদ ও উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর। তদুপরি অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা এবং তাপমাত্রার ক্রমবৃদ্ধির কারণে বহু প্রজাতির ফসলের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। আবার আগাছা, পরগাছা, রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অঞ্চলভেদে মাটির গুণাগুণ এবং উপাদানেও তারতম্য ঘটছে। ফলে ফসলের প্রত্যাশিত উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ইরি-বোরো উৎপাদনে অনেক সেচের পানির প্রয়োজন হচ্ছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জমিগুলোয় লবণাক্ততার কারণে সেচে, চাষে বিপত্তি ঘটছে। আবার লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে চিংড়ি চাষেও ধস নেমেছে।
অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলে সেচের পানিতে আরেক বিপত্তি ঘটছে। সেখানকার ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বেশি হওয়ায় ফসলের মাধ্যমে তা মানবদেহে প্রবেশ করছে। এ ছাড়াও উত্তরাঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় ফসলের জমিতে চাহিদা পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করা যাচ্ছে না। এ কারণে ফসল উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। এমনি অবস্থায় দ্রুতই জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি কমানো না গেলে শুধু দেশের নিম্নাঞ্চলই প্লাবিত হবে না, একই সঙ্গে মরুকরণের ঝুঁকিতেও বাড়বে। অন্যদিকে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে আমাদের বৃক্ষরাজি, বনজ, জলজ ও কৃষিজ, মৎস্য সম্পদের ওপরেও।
এমনি অবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা এবং এর বিরূপ প্রভাব থেকে পরিত্রাণে আমাদের নিজস্ব সম্পদ, মেধা, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা দিয়ে নিরন্তর গবেষণার মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের পথরেখা নির্মাণ, মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। একই সঙ্গে নদ-নদীর দূষণ, দখল রোধ এবং নাব্যতা ফিরিয়ে আনা জরুরি।
পাশাপাশি দেশের আনাচে-কানাচে খালি জায়গায় বনায়ন সৃষ্টি করতে হবে এবং অনাবাদি ও পতিত জমি দ্রুত চাষের আওতায় আনতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। পরিবেশ দূষণ বা বায়ুদূষণ ঘটে এমন ধরনের কাজকর্ম থেকেও আমাদের নিবৃত থাকতে হবে। একই সঙ্গে অতিমাত্রায় কার্বন নিঃসরণকারী তথা শিল্পোন্নত দেশগুলোর কাছে প্রামাণ্যচিত্রসহ আমাদের আর্জি তুলে ধরতে হবে।
এসব করা গেলে রাতারাতি জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করা সম্ভব না হলেও কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলবায়ুর ভয়াবহ অভিঘাতে বিপর্যস্ত আমাদের জীবনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের পাশাপাশি কৃষি, প্রকৃতি পরিবেশেও পরিবর্তন আসছে। এই পরিবর্তন ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের কৃষি, পরিবেশ, প্রতিবেশ, প্রকৃতিকে রক্ষায় একদিকে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রয়োজন কৃষির গবেষণা। প্রত্যাশা থাকবে সরকার এই বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে কৃষিজ উৎপাদন তথা কৃষিতে প্রযুক্তির প্রয়োগ ও অঞ্চলভিত্তিক ফল ফসল উৎপাদন, বিপণনে মনোযোগ দেওয়া এবং পরিবেশ, প্রতিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষায় আরও বেশি মাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা।