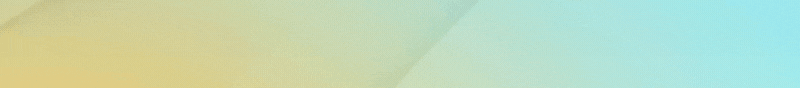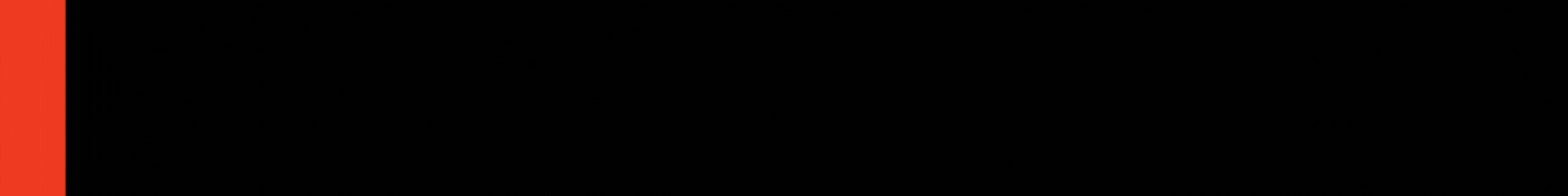অস্তিত্ব সংকটে সুন্দরবনের মুন্ডা আদিবাসী
- প্রকাশিত: সোমবার, ৩ নভেম্বর, ২০২৫
- ১১৫ বার পড়া হয়েছে

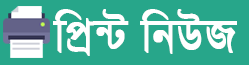
বিশেষ প্রতিনিধি : সুন্দরবনের ‘মুন্ডা’ আদিবাসীরা অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। বাংলাদেশের আদিবাসী বা উপজাতি জনগোষ্ঠীর কথা আসলে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ময়মনসিংহসহ হাতে গোনা কয়েকটি স্থানের নাম চলে আসে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু আদিবাসী সম্প্রদায় থাকলেও তেমন কারোর নজরে আসেনা।
সুন্দরবন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসরত মুন্ডা বা শর্না সম্প্রদায় এমনই একটি। মূলত তাদের পূর্ব পুরুষরাই বাঘের গর্জন আর সাপের ফনার তোয়াক্কা না করে জঙ্গল কেটে চাষবাস উপযোগী জমি বানিয়েছিল।
বর্তমান সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় জঙ্গল কেটে মনুষ্য বসতির জন্য উপযোগী করে তুলতে মুন্ডাদের পূর্ব পুরুষদের ভূমিকা ছিলো অনেক বেশি। বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল পরিবেশের কারণে সুন্দরবন ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুন্ডাদের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবে মুন্ডাদের নিজস্ব সংস্কৃতিও হুমকির সম্মুখীন।
মুন্ডারা নিজেদেরকে ‘হোরোকো’ বলে থাকে যার অর্থ মানুষ। তবে তারা নিজেদের মুন্ডা হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। মুন্ডা শব্দের অর্থ সম্মানী ও সম্পদশালী মানুষ। এদের আদি নিবাস বিহারের রাঁচিতে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দিতে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।
- সম্প্রতি এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ভারতে এদের সংখ্যা ১০ লাখের বেশি। ছোট নাগপুর ছাড়া মুন্ডাদের বাস ভারতের মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে। এছাড়া নেপাল ও বাংলাদেশে এরা ছটিয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে।
- বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মুন্ডা সম্প্রদায়ের বসবাস। সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ম্ন্ডুাদের সংখ্যা ১৫ হাজারের মতো, যাদের অধিকাংশ বসবাস করে বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায়। সবচেয়ে বেশি বাস করে নওগাঁ জেলায়। তবে কখন কিভাবে মুন্ডারা উত্তর বাংলায় এসেছিলো তার কোনো ঐতিহাসিক দলিল পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয়, মোগল আমল ও বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলে মুন্ডারা ব্যাপকহারে উত্তর বাংলায় চলে আসে।
ইতিহাসে উল্লেখ, মোগল শাসনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের আদিবাসীরা স্বাধীনতা ভোগ করেছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে মুসলমান শাসকরা ঝাড়খন্ডের মুন্ডাদের ওপর করারোপ করে। পরবর্তীতে বৃটিশ শাসনামলে ভূমিনীতি পরিবর্তনের কারণে মুন্ডাদের ভূমি মালিকানার ওপর বাজে প্রভাব ফেলে এবং মুন্ডাদের গ্রামীণ সম্প্রদায় ভেঙে যেতে থাকে।
জমিদার আর মহাজনদের অত্যাচার মুন্ডাদের বাধ্য করে চলে আসতে। ১৮৭২ সালের আদম শুমারিতে মুন্ডারা রাজশাহী জেলার আদিবাসী হিসেবে নথিভ্ক্তূ হয়। তবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মুন্ডাদের নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি এবং তারা কোনো পরিসংখ্যানেই নথিভ্ক্তূ নয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মুন্ডারা মূলত সুন্দরবন ও সুন্দরবন সংলগ্ন বৃহত্তর যশোর ও খুলনা জেলায় বসবাস করে। এই অঞ্চলে কিভাবে এসেছিলো তার সঠিক তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না।
এই অঞ্চলে তাদের আগমন নিয়ে লোকমুখে কিছু প্রচলিত তথ্য আছে যেমন-অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে জমিদারী প্রথার প্রচলন হলে জমিদাররা জঙ্গল পরিস্কার করার জন্য মুন্ডাদের সুন্দরবন অঞ্চলে নিয়ে আসে। অধিকাংশের ধারণা, মুন্ডা মজুররা সাপ বাঘ আর কুমিরের সাথে যুদ্ধ করে এই অঞ্চলটিকে চাষোপযোগী করে তুলেছিলেন।
দ্বিতীয় ধারনাটি হচ্ছে, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জের নলডাঙ্গার রাজা বিৃটিশ আমলে তাদেরকে নিয়ে আসেন। তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিলো লাঠিয়াল অথবা গৃহ পাহারাদার হিসেবে।
- আবার এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে, বৃটিশ আমলে এই অঞ্চলে নীল চাষ শুরু হলে নীল চাষীরা তাদের জমিতে কাজ করার জন্য নিয়ে আসে।
- মুন্ডাদের একটা বড় অংশ সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে বসবাস করে। মুন্ডা গবেষক শেখ মাসুদুুর রহমান তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন উপজেলার ৩০টি গ্রামে মুন্ডা আদিবাসী লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছেন।
এর মধ্যে রয়েছে- তালা উপজেলার বাকখালী, আসান নগর, হরিণখোলা, আড়োডাঙ্গি, কৃষ্ণনগর ও গাছা দুর্গাপুর। শ্যামনগর উপজেলার জেলেখালী, গাবুরা, পার্শ্বেমারী, ডুমুরিয়া, দাতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী, আবাদ চন্ডীপুর, মাগুরাকুনী, উত্তর কদমতলা, খ্যাগড়াঘাট, শ্রীফলকাটী, ধুমঘাট, তারানীপুর, ভেটখালী, পূর্ব কালিঞ্চী, পশ্চিম কালিঞ্চী, কাশিপুর, বাদঘাটা, কেওড়াতলী, সাপখালী ও শৈলখালী এবং খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার টেপাখালি, জোড়শিং, নোনাদিঘীর পাড়, বড়বাড়ি, কটকাটা, বতুল বাজার, আংটিহারা, পশুরতলা, মাজিবাইত, নলপাড়া, পাতাকাটা, গোয়ালখালি ও ঘটিরঘেরগ্রাম।
২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার ১২০টি পরিবারে মোট মুন্ডা সংখ্যা ৫৪০। কয়রা উপজেলায় বসবাসকারী মুন্ডাদের সংখ্যা ৩২০টি পরিবারে ১৫৩০ জন। শ্যামনগর উপজেলায় বাস করে ৩৫৩টি পরিবারের ১৭৭০ জন। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, মুন্ডাদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।
৪০-৫০ বছর পূর্বে যত মুন্ডা ছিলো, এখন সে সংখ্যাটি অনেক হ্রাস পেয়েছে। যারা এখনো আছে তাদের ভাষ্যমতে, তাদের একটি বড় অংশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার শিকার হয়ে সুন্দরবন অঞ্চল ত্যাগ করে বিভিন্ন এলাকায় চলে গেছেন।
যে অল্প সংখ্যক মুন্ডা অধিবাসী আছেন তারাও হুমকির মুখে। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, বসবাসকারী মুন্ডাদের মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ জন মুন্ডা সামান্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। বাঙালিদের মতো মুন্ডারা কৃষি কাজে নিয়োজিত হলেও অধিকাংশই ভূমিহীন। মুন্ডাদের আর একটি পেশা দিনমজুরির ভিত্তিতে মাছ ধরা।
আদিবাসীরা যেহেতু খুব পরিশ্রমী তাই তাদেরকে স্বল্পমূল্যের শ্রমিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুন্দরবনের বন বিভাগ ও বহিরাগত ব্যবসায়ীরা বনের কাঠকাটা ও অন্যান্য কাজে নিয়োগ করে থাকে।
মাটির দেয়াল আর খড়ের ছাউনি দিয়ে তৈরি কুড়ে ঘরে তাদের বসবাস। ঘরের ভেতর সাপ, ইদুর আর তেলাপোকার উৎপাত তাদের নিত্য দিনের সাথী। মুন্ডারা যে সকল গ্রামে বাস করে সেখানে শুধু নোনাজল। সেখানে পানীয় জলের মারাত্মক অভাব রয়েছে। অনেক দূর থেকে মুন্ডা মেয়েরা খাওয়ার পানি আনতে হয় । এর উপর রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার প্রচন্ড অভাব।
- মুন্ডাদের খাবার ও পানীয়ের একটি ঐতিহ্যগত অভ্যাসের কারণে বাঙালিদের দ্বারা বর্ণবৈষম্যেও শিকার। তারা ইদুরের মাংস খায়। পঁচানো ভাত দিয়ে তৈরি মদ ছাড়া তাদের কোনো সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান কল্পনা করা যায়না। আর এই খাদ্যাভাসের কারণে মুসলমান ও হিন্দু বাঙালিরা তাদেরকে ভিন্ন চোখে দেখে। তাদেরকে অস্পৃশ্য বলে অবহেলা করে। তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কতো দূরের কথা তাদের বাড়িতে খাওয়াও অপরাধ মনে করে।
- মুন্ডাদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হলেও সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের ভূমিকাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তারা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। মুন্ডাদের ছেলেমেয়েরা হাঁটা আর কথা বলার শুরু সাথে নাচ-গান শিখে যায়।
মুন্ডা সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত। অনেক সময় অভিভাবকরা জন্মের পরপরই বিয়ে পাকাপাকি করে রাখে। ধারণা ও বিশ্বাস এ রকম যে, এভাবে বিয়ে দিলে ছেলেমেয়েরা জীবনটা দীর্ঘদিন উপভোগ করতে পারে। বিয়ে সাধারণত দেয়া হয় বৈশাখ ও ফাল্গুন মাসে।
মুন্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু বিবাহের প্রথা প্রচলিত। বহু বিবাহ নির্ভর করে কর্মক্ষমতার উপর। কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে সে তার দেবরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। দেবর অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলেও এই নিয়ম সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মহিলাদের ক্ষেত্রে কোনো স্ত্রী পরিত্যক্তা হলে সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে না, সারাজীবন একা একাই কাটাতে হয়।
মুন্ডা নারী-পুরুষ এক সাথে কাজ করে। কৃষি কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরা বেশি কুশলী। এমনকি নারীরা মাছ ধরতেও অনেক বেশি পারদর্শী।
সুন্দরবনের মুন্ডাদের নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন শেখ মাসুদুর রহমান, যিনি বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর যুগ্ম পরিচালক। রাইজিংবিডির সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, মুন্ডা সম্প্রদায়ের লোকেরা দীর্ঘদিন অবহেলার শিকার হওয়ায় সমাজের অন্যান্য সম্প্র্রদায় থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে এমনকি ন্যূনতম মৌলিক অধিকারগুলো থেকে তারা বঞ্চিত। তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতে আনার জন্য সরকারি-বেসরকারি ব্যাপক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।
বিশ্বায়নের এই যুগে সবাই যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন মুন্ডাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন নেই। তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। যুগযুগ ধরে বসবাসরত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মুন্ডাদের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন বলে স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।
আদিবাসী মুন্ডা নারীরা দলবেঁধে এভাবেই গান গেয়ে গেয়ে মাঠেঘাটে কাজ করে। তাঁরা শামুক খোটে, মাটি কাটে, মহাজনের জমিতে কাজ করে। ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত তাঁরা। সামাজিক এমন নানা বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার এসব আদিবাসীরা এখন সমাজের মূলধারার উঠে আসার চেষ্টা করেছে। তাঁরা ভোট দিচ্ছে, লেখাপড়া শিখছে, যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরিও করছেন। তবু সামাজিকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে তাঁরা।
আদিবাসী মুন্ডা নারীদের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মানার আগ্রহ কম। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মোটেও সচেতন ছিলেন না তাঁরা। সেই এখনও অনেকেই প্রাচীন ধ্যান-ধারণা পোষণ করলেও সাম্প্রতিককালে মুন্ডা নারী-পুরুষরা জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অনেকটাই সচেতন হয়ে উঠছে।
জানা যায়, দুইশ বছর আগে ভারতের রাঁচিসহ বিভিন্ন স্থান থেকে আসা আদিবাসী মুন্ডারা সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করে। তখন থেকেই সুন্দরবনকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে মুন্ডাদের জীবন জীবিকা। এসব জমি তাঁরা আদিকাল থেকে নিজেদের হিসেবে ভোগ দখল করলেও এখন পর্যন্ত এই জমিতে তাদের দালিলিক স্বত্ব নেই। ফলে তাঁরা এসব জমি কারও কাছে বিক্রি করতে পারে না। কেউ কিনতেও পারে না।
এক সময় মুন্ডারা সুন্দরবনের হরিণ, শুকর, সাপ, বনমোরগসহ বিভিন্ন প্রাণী শিকার করতেন। সেসব প্রাণী নিজেরা খাওয়ার পাশাপাশি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতেন। তবে বন্যপ্রাণি নিধন আইন প্রচলিত হওয়ার পর, সাতক্ষীরা অঞ্চলের মুন্ডারা সেসব পেশা থেকে সরে এসেছেন। বর্তমানে তাঁরা সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরে, কাঁকড়া ধরে, এমনকি বনবিভাগের পাস-পারমিট (অনুমতি) পেলে মধু আহরণ ও জোংড়া খোটার কাজও করেন। মুন্ডা পরিবারের নারী-পুরুষ সবাই সমান তালে কাজ করেন। ঘেরে মাছ ধরা, মাছ চাষ করাসহ কৃষিভিত্তিক নানা কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে মাঠেঘাটে তাদের কাজের দাম কম। তারা একদিন কাজ না করলে পরদিন সংসার চালাতে পারে না।
সাতক্ষীরা জেলায় প্রায় সাড়ে পাঁচশ মুন্ডা পরিবার রয়েছে বলে জানা যায়। তাদের সদস্য সংখ্যা চার হাজারের কম নয়। সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার কাশিপুর, সাপখালি, কচিখালি, তারানিপুর, ধুমঘাট, কালিঞ্চি, মুন্সিগঞ্জ, রমজান নগর, তালা উপজেলার বাগডাঙ্গা আড়ুয়াখালিসহ বিভিন্ন স্থানে তাদের বসতি রয়েছে। এছাড়াও খুলনার কয়রা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে তাদের বসতি রয়েছে। এসব বসতিতে তাঁরা নিজেদের মতো করে বাড়িঘর তৈরি করে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে।
সাতক্ষীরার মুন্ডা পরিবারগুলোতে লেখাপড়ার সুযোগ কমই ছিল। জেলার শ্যামনগর উপজেলার কাশিপুর গ্রামের কৃষ্ণপদ মুন্ডাই ছিলেন প্রথম যুবক, যিনি উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পাস করেন। পরে সাতক্ষীরার বংশীপুরের গির্জার ফাদার লুই পাজ্জির সহায়তায় কৃষ্ণপদ মুন্ডা তাঁর গ্রামে গড়ে তোলেন একটি প্রাথমিক শিক্ষালয়। সেখানে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের একাই পড়াতেন তিনি। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য বইখাতা, কাগজ, কলম সরবরাহ করতেন ফাদার লুই পাজ্জি। শিক্ষক কৃষ্ণপদ মুন্ডার মাসিক বেতনও দিতেন লুই পাজ্জি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে মুন্ডা বসতি এলাকায় কমিউনিটি স্কুল তৈরি হয়েছে। সেখানে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়েও শিশুরা লেখাপড়া করে। সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া উপবৃত্তি পায় মুন্ডা শিশুরা। এমনকি বিনামূল্যে লেখাপড়া, স্কুলের খাদ্য সহায়তা, বই-খাতা থেকেও বঞ্চিত নয় বর্তমানের শিক্ষার্থীরা।
কৃষ্ণপদ মুন্ডা ও লুই পাজ্জি প্রথম শিক্ষার আলো ছড়িয়েছিলেন মুন্ডা পাড়ায়। এছাড়াও লুই পাজ্জি শ্যামনগরের মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের কচিখালিতে, তালার বাগডাঙ্গা, আড়ুয়াডাঙ্গা, মুন্নাসহ বিভিন্ন এলাকার মুন্ডা বসতিতে নতুন নতুন ঘর তৈরি করে দিয়েছেন। সাতক্ষীরার অধিকাংশ মুন্ডাদের বসবাস ছোট ছোট ভাঙাচোরা ঘরে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের এসব বসতঘরের খানিকটা উন্নতিও হয়েছে। এছাড়া মুন্ডা সদস্যদের অনেকেই পেয়েছেন দেওয়া সরকারের দেওয়া নতুন ঘর। মুন্ডা জনগোষ্ঠী সেখানে অনেকটাই আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে। তবে অধিকাংশ মুন্ডাদের ঘরবাড়ি এখনও মাটির। গরান কাঠের বেড়া আর গোলপাতার ছাউনির ঘরে তাদের বসবাস।
শ্যামনগরের মুন্ডা বসতিতে রয়েছে খাবার পানির সংকট। লবণাক্ত এলাকা হওয়ায় সেখানে টিউবওয়েল বসানো হয় না। তবে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা একাধিক মুন্ডাপাড়ায় পানির ড্রাম বসিয়ে দিয়েছে। এসব পাত্রে মুন্ডারা বৃষ্টির পানি ধরে রেখে তা সারাবছর পান করে। খাবার পানির সংকট দেখা দিলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে পানি সংগ্রহ করে মুন্ডা নারীরা। পুকুরের পানি অথবা পিএসএফ (পন্ড স্যান্ড ফিল্টার) থেকেও খাবার পানি সংগ্রহ করে তারা।
মুন্ডাদের রয়েছে নিজস্ব ধর্মীয় আচার। মুন্ডারা শারুল পূজা, কারামপূজা এবং মনসাপূজা করে থাকেন নিজেদের মন্দিরে। এরা বিভিন্ন পূজাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে হাড়িয়া মদ ব্যবহার করে থাকে বলে জানা যায়। মুন্ডাদের খাদ্যতালিকায় রয়েছে শামুক, ইঁদুর, জোংড়া, ঝিনুক, কাঁকড়া, কুচে, কচ্ছপ ইত্যাদি। তবে রুচিভেদে এসব খাবার খান মুন্ডারা। মুন্ডাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। তাঁরা সাদৃ ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলে। এ এলাকায় মুন্ডা ছাড়াও মাহাতো এবং উরাও সম্প্রদায়ের সদস্যরা রয়েছেন।
মুন্ডারা এখনও মহাজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁরা মহাজনদের থেকে ঋণ নেয়। বছর শেষে নির্দিষ্ট সময়ে সেই ঋণ তাদের পরিশোধ করতে হয়। মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করা মুন্ডারা পুণ্যের কাজ মনে করে। তবে এই সুযোগে মহাজনরা তাদের থেকে অর্ধেক দামে মাছ, কাঁকড়া কিংবা শস্যদানা কিনে নেন। একরকম শ্রমদাস হিসেবে মহাজনদের নিয়ন্ত্রণে থাকে মুন্ডারা।
মুন্ডা তরুণ তরুণীরা শ্যামনগর উপজেলা সদরে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এসব প্রশিক্ষণ শেষে তাঁরা কর্মক্ষেত্র বেছে নিচ্ছি। তবুও সামাজিকভাবে তাঁরা নানা বৈষম্যের শিকার। তারা বিয়েবাড়িতে কিংবা অন্যকোনো অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ পায় না। যদিও বা পান তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি হোটেল-রেস্তোরাঁয় তাঁরা খেতে বসলে নানা বৈষম্যের শিকার হন। কোনো কোনো সময় তাঁরা অন্যদের পুকুরের পানি ব্যবহারের সুযোগ পান না।
সাতক্ষীরার শ্যামনগরে আদিবাসী মুন্ডাদের একটি সংগঠন রয়েছে ‘সামস’। এই সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা মুন্ডা পরিবারগুলোকে দেখভাল করে। মুন্ডাদের সামাজিক অধিকার আদায়ে সংগঠনটি আন্দোলন করে থাকে। সংগঠনটির সভাপতি কালিঞ্চী গ্রামের গোপাল মুন্ডা জানান, ‘এখন আগের অবস্থা নেই। আমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করছে, প্রশিক্ষণ পাচ্ছে, যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরিও পাচ্ছে।’
গোপাল মুন্ডা বলেন, ‘সামাজিক বৈষম্যও অনেকটা দূর হয়েছে। তবুও মূল ধারার জনগোষ্ঠীদের সঙ্গে আমরা এখনও পুরোমাত্রায় নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারিনি।’
সামসের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণপদ মুন্ডা জানান, মুন্ডাদের মরদেহ বেশিরভাগ সমাধিস্থ করা হয়। তবে জায়গার সংকটের কারণে অনেক ক্ষেত্রে তাদের শ্মশানে দাহ করা হয়ে থাকে।
মুন্ডা প্রতিনিধি রতিকান্ত মুন্ডা বলেন, ‘মুন্ডা নারীরা সেলাইসহ বিভিন্ন হাতের কাজ করেছে। এতে তাঁরা অর্থ উপার্জন করে থাকে। শ্যামনগরের কালিঞ্চি গ্রামে মুন্ডারা গড়ে তুলেছে ম্যানগ্রোভ ভিলেজ। সেখানে একটি মিনি পর্যটন কেন্দ্রও গড়ে তুলেছে তাঁরা। পরিবেশবান্ধব এই পর্যটন ভিলেজের উন্নয়নে সরকারি কোনো সহযোগিতা পায়নি মুন্ডারা।’
রতিকান্ত মুন্ডা জানান, শ্যামনগরের আটটি ইউনিয়নেই রয়েছে আদিবাসীদের বসবাস। ফাদার লুই পাজ্জি তাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা দিচ্ছেন। জমির দালিল না থাকার সুযোগে প্রভাবশালীরা মুন্ডাদের জমি দখল করে নিয়েছে। এ নিয়ে শ্যামনগরে বেশ কয়েকটি ঘটনাও ঘটেছে।
মুন্ডারা আশাবাদ জানায়, ৯ আগস্টের বিশ্ব আদিবাসী দিবসে আবারও উচ্চারিত হবে তাদের ভূমি অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক সাংস্কৃতিক অধিকারের কথা।
আদিবাসীরা তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন করে যাচ্ছে। তাঁরা ভূমির অধিকার দাবি করেছে। এসব জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় নিয়ে আসতে হলে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে বলে জানান আদিবাসী মুন্ডারা।