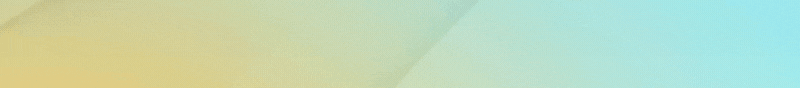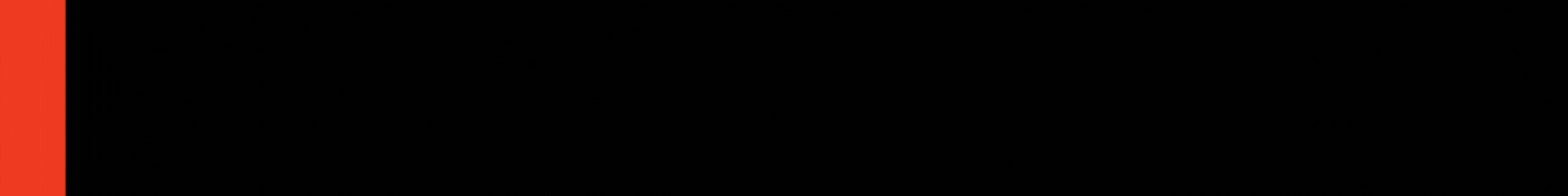বিপন্ন প্রাণ, বিলুপ্ত প্রজাতির এত কান্না পৃথিবী রাখবে কোথায়?
- প্রকাশিত: বৃহস্পতিবার, ৬ নভেম্বর, ২০২৫
- ২৯২ বার পড়া হয়েছে

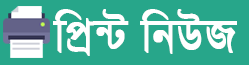
সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : একটি সত্যি রূপকথার গল্প দিয়ে বিষয়টির অবতারণা করা যাক। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে মোহো ব্র্যাকাটার্স নামে এক প্রজাতির পাখি ছিল। হ্যাঁ, কোনো একসময় ছিল, এখন আর নেই। বাঁশির সুরের মত বিষণ্ণভাবে ডাকে বলে এদের চলতি নাম কোয়াই ও-ও। এই বিরলতম প্রজাতির পাখি কমতে কমতে আটের দশকে গোটা পৃথিবীতে মাত্র দুটি কোয়াই ও-ও বেঁচে থাকে, একটি পুরুষ, আরেকটি নারী। পরিবেশবিদদের আশা ছিল এই জুটি থেকেই ধীরে ধীরে আবার প্রজাতিটির বংশবৃদ্ধি হবে, বিলুপ্তির দোরগোড়া থেকে ফিরে আসবে প্রাণচঞ্চল প্রকৃতির মাঝে। কিন্তু বিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যে ক্রূর হাসি হাসছিলেন। এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারা যায় একমাত্র জীবিত নারী পাখিটি। সঙ্গিনীকে হারিয়ে পুরুষ কোয়াই শুধুই ও-ও করে করুন সুরে ডেকে চলে। বৃষ্টির মধ্যে, বাজের শব্দের মধ্যেও তার আকুলি বিকুলি ধ্বনিত হয়েছে এক গাছ থেকে আরেক গাছে। ছড়িয়ে পড়েছে পুনর্মিলনের বিফল আকুতি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাঁশির বিষন্ন সুর হাওয়াই দ্বীপের ঘন জঙ্গলের প্রান্তরে প্রান্তরে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে ফিরে এসেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য কোয়াই ও-ও প্রজাতির শেষ সদস্যটিও একদিন মারা গেলেন সঙ্গিনীকে খুঁজে পাওয়ার নিষ্ফল আশা নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, পাখিদের ধ্বনি-সুর-গান নিয়ে একটি অপূর্ব সুন্দর ছবি (সাউন্ড ৩২) বানিয়েছেন আমেরিকান চলচ্চিত্র নির্মাতা স্যাম গ্রিন। প্রজাতির শেষ সদস্যের মৃত্যুর তিন দশক পর এই ছবিতে কান্নার সুর ধ্বনিত হলে প্রেক্ষাগৃহে শ্রোতা দর্শকদের হৃদয়ও যেন দুমড়ে মুচড়ে ওঠে।
আর একটি সত্যি রূপকথার ইতিবৃত্ত শুনে নেওয়া যাক। এক যে ছিল ডোডো, টার্কির চেয়েও বড়। সে পারত না উড়তে। কেমন ছিল ওদের রূপকথার দেশ? Dodo (Raphus cucullatus), এক বিলুপ্ত পাখি, সাকিন ছিল ভারত মহাসাগরের মরিশাস দ্বীপ। একটি পূর্ণবয়স্ক এই পাখির ওজন প্রায় ২৩ কেজি। পাখি প্রজাতির হলেও ডোডো উড়তে পারে না, কিন্তু দেখতে ভারি সুন্দর। নীল-ধূসর শরীরে একটি বড় মাথা, ৯ ইঞ্চি মাপের কালো রঙের বিলের সাথে লাল রঙের আবরণ যা হুকযুক্ত মোটা ও তীক্ষ্ণ ঠোঁটের জন্ম দিয়েছে, সাথে ছোট অকেজো ডানা, শক্ত হলুদ পা, এবং কোঁকড়ানো একগোছা উঁচু পালক পিছনের প্রান্তে বিরাজ করে। ভারত মহাসাগর এবং এর ভাসমান দ্বীপগুলি অসংখ্য ছোট বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল। এই অঞ্চলে এমন অনেক দ্বীপ রয়েছে, যেখানে কয়েক শত বছর ধরে ‘সভ্য মানুষ’ পদার্পণ করেনি। অন্তত ১৫০৫ সাল পর্যন্ত, মরিশাস এমন একটি জনবসতিহীন দ্বীপপুঞ্জ ছিল। সেখানে জঙ্গল ছিল ঘন, গভীর। সেই দ্বীপের খোলা তৃণভূমি ও ঘন জঙ্গলে নিরাপদে নিশ্চিন্তে নির্বিবাদে বিচরণ করত ডোডো পাখিদের দল।
আপনাদের সাহায্য আমাদের বিশেষভাবে প্রয়োজন। স্বাধীন মিডিয়া সজীব গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে কথাগুলো বলা আবশ্যক এবং যে প্রশ্নগুলো তুলতে হবে, তার জন্যে আমরা আমাদের পাঠকদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।
নাগরিক ডট নেটে সাবস্ক্রাইব করুন।
গাছের ফল খেয়েই সুখে দিন কাটত তাদের। ওই দ্বীপে তাদের কোন শত্রু ছিল না। না মানুষ, না অন্য প্রাণ প্রজাতি। তারা পাখি, কিন্তু জীবনের অভিযোজনে তারা উড়তে পারে না, কারন তাদের ওড়ার প্রয়োজন হয়নি। ডোডোদের বিলুপ্তির কারণ সভ্য মানুষের অপার খিদে, যে খিদে প্রকৃতির এই সুন্দর নিরীহ প্রাণীকেও যাদুঘরে পাঠিয়ে ছেড়েছে। ১৫০৭ সালের দিকে পর্তুগিজ নাবিক মরিশাসে পদার্পণ করে সন্ধান পায় ডোডো পাখির। ডোডো নিধন শুরু হয় তার সুস্বাদু মাংসের লোভে। সমুদ্রযাত্রার রসদ হিসেবে ডোডোদের ধরে নিয়েও যাওয়া হয়। এরা এত বোকা ছিল যে, মানুষ তাদের ধরতে এলে পালিয়ে না গিয়ে বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে আসতো, একদল নিহত হলে আর এক দল। হায় রে ডোডো! বুঝলি না মানুষের চরিত্র! এরপর মানুষ এই দ্বীপে থাবা গেড়ে বসে, নিজেদের ও সাথে নিয়ে আসা শূকর, ইঁদুরের মতো পশুদের প্রধান খাদ্য হয়ে ওঠে পাখির মাংস আর সুবৃহৎ ডিম। এর আগে ডোডো শিকার করার কোন মানুষ বা খাদ্যশৃঙ্খলের অন্যকোনো প্রাণীও ছিল না মরিসাস দ্বীপে। সত্যি রূপকথার দেশে ডোডোরা নির্বিঘ্নে নিরাপদে সুখের দিন কাটাইত। লোভী মানুষের দল জঙ্গলের ফসল ও গাছ কাটা চালিয়ে গেল নির্বিচারে। শুরু হল নতুন পরিচিত মানুষ ও প্রাণীদের কাছে ডোডোদের হেরে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। এই অসম লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হতে বাধ্য হয়। অভিধানে আজ ‘বিলুপ্তি’ আর ‘ডোডো’ কথা দুটি সমার্থক হয়ে রয়ে গেছে।
ডোডো পাখি ১৬৮১ সাল নাগাদ পৃথিবীর ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেল। কিন্তু এই গল্পের শেষ হবে আরও এক করুন বিয়োগান্তক পরিণতির মধ্য দিয়ে। এর বিলুপ্তির একটি ভয়ানক প্রভাব পড়ে বাস্তুতন্ত্রের উপর। একজন বিজ্ঞানী লক্ষ্য করলেন, মরিশাসে একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির গাছ (tambalacoque) বিরল হয়ে যাচ্ছে। এই প্রজাতির অবশিষ্ট ১৩টি গাছের সবকটিই প্রায় ৩০০ বছর বয়সী। ১৬০০ শতকের শেষের দিক থেকে এই প্রজাতির কোনো নতুন গাছের জন্ম হয়নি। যেহেতু এই গাছের গড় আয়ু ছিল প্রায় ৩০০ বছর, প্রজাতির শেষ সদস্যরা ছিল অত্যন্ত পুরনো। গাছটি ৩০০ বছর আগে প্রজনন বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তা ডোডোদের বিলুপ্তির সময় থেকেই। না, এটা কাকতালীয় ঘটনা নয়। বরং একটি প্রাণ প্রজাতি হারিয়ে যাওয়ার সাথে এই গাছের শেষ হয়ে যাওয়ার মধ্যে এক অদৃশ্য সূক্ষ্ম সুতোর টান আছে। গবেষণালব্ধ ফল জানাচ্ছে: এই গাছের ফল খাওয়ার পর ডোডোর পাচনতন্ত্রে সেই বীজগুলি সক্রিয় হয়ে উঠত এবং তা পাখির মলের মধ্য দিয়ে মাটিতে পড়ে আবার লকলকিয়ে বেড়ে উঠত। অভিযোজনের বিজ্ঞান মেনে সেই গাছের বীজ অন্য কোন পাখি বা প্রাণীর অন্ত্রে আর সক্রিয় হতে পারেনা। তাই এই গাছটিও পরিচিত হয়ে ওঠে একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার ৩০০ বছরেরও বেশি সময় পরে, আরেকটি করুন পরিণতির মধ্য দিয়ে। আসলে এটাই প্রকৃতির নিজস্ব জগতে সহমর্মিতা, যুথবদ্ধতা ও মিথোজীবিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রকৃতির একটি অংশে আঘাত করলে অন্য অঙ্গগুলোও বিপদগ্রস্ত হয়। তাই আমাজনের গহীন অরণ্যে অনাবৃষ্টির ফলে মৌমাছির দল ডানা না ঝাপটালে, তার হাত ধরে আমাদের খাদ্য ভান্ডারেও টান পড়ে।
বিভিন্ন গবেষণা থেকে উঠে আসা তথ্য বলছে, অন্তত ৮৭ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবীতে মানুষের প্রাণ ধারণের প্রাথমিক সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে। কিন্তু অপরিকল্পিত ও অবৈজ্ঞানিক ‘উন্নয়নের’ খাতিরে স্থলভূমির শতকরা ৭৫ ভাগ আর সমুদ্রের শতকরা ৬৬ ভাগ স্বাভাবিক পরিবেশ আজ ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। বিজ্ঞানী,পরিবেশবিদদের মতে, নয়া বিশ্বে কমে যাবে মানব বান্ধব উদ্ভিদ ও প্রাণী। বর্তমান গতিতে উষ্ণায়ন, উন্নয়ন, আর বনভূমি পাহাড় জঙ্গল জলাভূমি সহ প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করে নগরায়ন চলতে থাকলে, আকাশ বাতাস জলের দূষণ বাড়তে থাকলে, বছর দশেকের মধ্যেই অন্তত চল্লিশটি প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি নতুন করে বিলুপ্ত হবে। বিপন্ন বিপদগ্রস্ত হবে আমাদের চেনাজানার ৭০ শতাংশ পাখি, হাতে পড়ে থাকবে শুধুই পেন্সিল। ‘ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার’ এর লিভিং প্লানেট রিপোর্ট, ২০২২ থেকে জানা যাচ্ছে: পৃথিবীতে প্রাণী প্রজাতির প্রায় অর্ধেক বিনাশের মুখে। মানুষের নানান অপ্রাকৃতিক অবৈজ্ঞানিক কাজের চাপে এদের বাসভূমি ক্রমশ কমে আসাটাই মূলত এর জন্য দায়ী। সমীক্ষকরা পাঁচটি প্রাণী ও পোকামাকড় সমেত ৬ হাজারের বেশি প্রজাতির জনঘনত্ব পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ৪৮ শতাংশ প্রজাতির জনসংখ্যা ক্রমশ কমছে। আগামী দিনে যা আরও দ্রুতগতিতে কমবে। উভচর প্রজাতির ৬৩% এবং সরীসৃপ প্রজাতির ২৮% প্রাণী হারিয়ে যেতে বসেছে। অন্যদিকে ‘ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেশন অফ নেচার’ এর লাল তালিকাভুক্ত প্রায় ২৮% প্রাণী বর্তমানে বিনাশের মুখোমুখি। এই পৃথিবীতে মানুষের দখলদারি ও ভোগ বাড়ছে। সমান তালে কমছে বৃহৎ প্রাণ, ক্ষুদ্রজীব, অনুজীব ও কীটপতঙ্গের সংখ্যা। হারিয়ে যাচ্ছে কত শত প্রাণ প্রজাতি।
লোভ আর হিংস্রতা বোঝাতে যে প্রাণীটির উদাহরণ দেওয়া হয়, সেটা হায়েনা। রাজশাহীর বরেন্দ্র এলাকার ঊষর লাল মাটিতে উনিশ শতকের শেষের দিকেও ঘুরে বেড়াত ধূসর হায়েনার দল। এখন বাংলাদেশের কোথাও আর হায়েনা নেই। একসময় এ দেশে গন্ডারও ছিল। গত ১০০ বছরে বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে এমন ৩১ প্রজাতির প্রাণী। বাংলাদেশের ১,৬১৯ প্রজাতির বন্যপ্রাণীর কোনটির কী অবস্থা, সে-বিষয়ক লাল তালিকা তৈরি করা হয়েছে বনবিভাগ এবং প্রকৃতি সংরক্ষণ-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার’ এর যৌথ প্রয়াসে। এই তালিকা তৈরিতে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। নতুন তালিকায় দেখা যায়, দেশের ৩৯০টি বন্যপ্রাণী কোন না কোনভাবে বিপন্ন। ২০০০ সালের প্রথম তালিকায় দেখা যায়: এর আগের ১০০ বছরের মধ্যে ১৩ প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (তথ্যসূত্রঃ প্রথম আলো, অনলাইন পত্রিকা)। ২০২৩ এর তথ্য: পাঁচ দশকে দেশের বন থেকে হারিয়ে গেছে ৩১ প্রজাতির বন্যপ্রাণী। বিলুপ্তির মুখে রয়েছে হাতি, বাঘ, ভাল্লুক, অজগর, রাজ গোখরো, গয়ালের মতো প্রাণী। গবেষকরা বলছেন, দেশের দেড় হাজার প্রজাতির বন্যপ্রাণীর ২০ ভাগ রয়েছে বিলুপ্তির দোরগোড়ায়।
এই সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে: এক সময় ১২ শিঙা হরিণ ছিল সিলেটের বনে। বুনো মহিষ, নেকড়ে সহ ১১ স্তন্যপায়ী, ১৯ প্রজাতির পাখি ও কুমিরসহ ৩১ প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে গত ৫০ বছরে। উদ্ভিদের পরাগ মিলনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম মৌমাছি। ফলমূল, শাকসব্জির শতকরা ৭০ ভাগের জন্ম এদের মাধ্যমে। মৌমাছিকে পরিবেশের বন্ধু বলা হলেও এদের অস্তিত্ব এখন চরম হুমকির মুখে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বায়ু দূষণ, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অধিক পরিমাণে কীটনাশকের ব্যবহারে মৌমাছি বিলুপ্তির মুখে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মনোয়ার হোসেন বলছেন –“দেশে ২০ প্রজাতির মৌমাছির মধ্যে সচেয়ে ঝুঁকিতে সুন্দরবন ও পাহাড়ি এলাকার মৌমাছি।” উত্তরে তিস্তার অববাহিকা, দক্ষিণ-পশ্চিমে সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি ছিল তিন প্রজাতির গণ্ডারের। কালের বিবর্তনে দেশের প্রকৃতি থেকে হারিয়ে গেছে স্তন্যপায়ী তৃণভোজী এই প্রাণীটি। গত শতকে দেশের তৃণভূমিতে আবাস ছিল ময়ূর প্রজাতির পাখি পাতি ডাহরের, সেটি এখন নেই হয়ে গেছে। (তথ্যসূত্র: https://www.greenpage.com)।
সুন্দরবন বলতেই মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে এক বিস্তীর্ণ সবুজ বনভূমি, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বাসভূমি। চিতল হরিনের ছোটাছুটি, বানর দলের এ গাছ থেকে ও গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা, অসংখ্য পাখপাখালির কলরব। ‘জলে কুমির ডাঙায় বাঘ’: প্রবাদটির উৎপত্তিই হয়েছে সুন্দরবনের বিপদসঙ্কুল জঙ্গল ও জলাভূমির কথা মাথায় রেখে। ভয়ঙ্কর সুন্দর এই সুন্দরবন: এশিয়ার সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ জঙ্গল। সুন্দরী গাছের আধিক্যের কারণে এই জঙ্গলের নাম হয়েছে ‘সুন্দরবন’। আমাদের চিরচেনা সুন্দরবন কিন্তু আগে এইরূপ ছিল না। এখন সুন্দরবনে যেসকল প্রাণী আছে আগে এর থেকে বহু প্রজাতির প্রাণী ছিল, যেগুলোর অনেকেই এখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। মানুষের লোভের বশে, প্রকৃতির প্রতিকূলতায় আর খাদ্যসংকটে তারা পুরোপুরি মুছে গেছে সুন্দরবন থেকে। গাঙ্গেয় শুশুক (Gangetic Dolphin): আমরা ছোটবেলায় অনেকেই দেখেছি বড় কোন নদীতে নৌকায় বেড়ানোর সময়। গাঙ অর্থাৎ নদীতে এদের পাওয়া যায় তাই নাম গাঙ্গেয় শুশুক। খুবই নিরীহ জাতের এইসব শুশুক শুধুই মাছ খায়। সুন্দরবনের বড় নদীগুলোতে অত্যধিক জলদূষণের কারণে এরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এছাড়া আরও বহু প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে আছে বেশ কয়েক প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ, জলাশয়ের কচ্ছপ, ঘড়িয়াল, গোসাপ, কাঁকড়া, দুই তিন রকমের ভোঁদড়, হনুমান, বেশ কয়েক প্রজাতির বন বেড়াল, অসংখ্য প্রজাতির পাখি ও মাছ। আমাদের গর্ব যে বাঘ, সেও আজ বিলুপ্তির পথে। কর্পোরেটের হানাদারি, জঙ্গল পাহাড় ধ্বংস করে খনিজ উত্তোলন এবং তার হাত ধরে পরিবেশ দূষণ যদি এভাবে দিন দিন বাড়ে, তাহলে সেদিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন আমাদের গর্বের “Royal Bengal Tiger” শুধুমাত্র বইয়ের পাতাতে ছবি হিসাবে ঠাঁই পাবে। (তথ্যসূত্র: https://steemit.com/hive)।
দুই বাংলার মানুষের কাছে ও দুই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে সুন্দরবনের গুরুত্ব অপরিসীম। দশ হাজার বর্গকিলোমিটার ব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মনোরম সুন্দরবন একদিকে দুই বাংলা তথা ভারতের ফুসফুস। ৬৪ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ, লতাগুল্ম, ঘাস ও সমুদ্রের নিচে বসবাসকারী কোটি-কোটি ফাইটোপ্লাংটন সমৃদ্ধ এই সুন্দরবন বাতাসের বিষাক্ত কার্বন- ডাইঅক্সাইড শুষে নিয়ে প্রাকৃতিক কার্বন-সিঙ্ক হিসেবে কাজ করে, যোগান দেয় মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান রসদ অক্সিজেন। অন্যদিকে একের পর এক আছড়ে পড়া দানবীয় ঝড়ঝঞ্জা থেকে কলকাতা সহ দুই বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে রক্ষা করে চলেছে সুন্দরবন তার নিজের শরীর দিয়ে। উল্লেখ্য দুই বাংলা মিলে মোট আয়তনের মোটামুটি ৩০% বনাঞ্চল আছে, এর সিংহভাগই আছে সুন্দরবনে, যা বাংলাদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব ভারতের জলবায়ুকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে। একটি তথ্য ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে যে, মুঘল ও ইংরেজ আমলে সাড়ে তিনশ’রও বেশি সামুদ্রিক ঝড় আছড়ে পড়েছে সুন্দরবনে। সুন্দরবনবাসী ও কলকাতা শহরকে সেইসব ঝড়ের বীভৎসতা থেকে বাঁচিয়ে ছিল সুন্দরবন তার বুক আগলে। একজন বিজ্ঞানী আধুনিক পরীক্ষা-পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখিয়েছেন– সুন্দরবন তার শরীরের ৩০% ক্ষতির বিনিময়ে জনবসতি আর বন্যপ্রাণকে বাঁচিয়েছে, না হলে এক দানবীয় ‘সিডার’ ঝড়েই বাংলাদেশের মতো তথাকথিত দরিদ্র দেশে গোটা সুন্দরবন উজাড় করে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিটেমাটি হারিয়ে দেশান্তরী হতে বাধ্য হতেন। দুই বাংলা সহ দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের ফুসফুস ও ঝড়ঝঞ্জা থেকে মানুষকে রক্ষা করার প্রাচীর এই সুন্দরবন এখন আর সুন্দরী নেই।
মানুষের লোভ লালসা, জঙ্গল ধ্বংস করে তথাকথিত ইকোট্যুরিজম আর উন্নয়নের ঠেলায় সে আজ গভীর রোগে আক্রান্ত। হিমালয় থেকে উৎপন্ন গঙ্গা নদীর শত শত শাখা নদী-উপনদী দিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে বয়ে নিয়ে আসা পলি বালি দিয়ে বঙ্গোপসাগর উপকূলে তৈরি হয়েছিল বিশাল বদ্বীপ, যা গাঙ্গেয় বদ্বীপ নামে খ্যাত। এই বদ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম হলেও বয়সে নবীনতম, যা পুরোপুরি গড়ে ওঠার আগেই ব্রিটিশ আমলে নির্বিচারে জঙ্গল কেটে অবিভক্ত বাংলার গোটা সুন্দরবনের এক বড় অংশজুড়ে চাষের জমি তৈরি ও বসতি স্থাপন হল। জোয়ারের উপচে পড়া লবণাক্ত জল থেকে জনবসতিকে বাঁচাতে গড়ে উঠল নদী বাঁধ। “একূল ভেঙে ওকুল গড়ে” নদীর এই স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে সুন্দরবনের প্রকৃতি পরিবেশের উপর প্রথম কোপটা নামিয়ে আনল তথাকথিত উন্নত সভ্য সমাজ।বাংলাদেশে সুন্দরবনের প্রধান নদী গরাই সবচেয়ে বেশি মিঠা জল আর পলি বয়ে নিয়ে আসত পদ্মা থেকে, যা জলে লবনের ভারসাম্য রক্ষা ও নতুন ভূভাগ তৈরিতে সাহায্য করত। ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরির পর থেকেই পরিস্থিতি বদলে গেল। সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়িগুলোতে মিষ্টি জলের সরবরাহ কমে লবণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় একদিকে যেমন সুন্দরবনের মানুষের পানীয় জলের সংকট দেখা দিল, অন্যদিকে ‘টপ ডাইয়িং’ জাতীয় রোগে গত ২৫ বছরে শুধু সুন্দরী গাছ কমেছে প্রায় ৫০%। প্রতিদিন কমছে গরান গেওয়া ধুন্দল সহ নানা প্রজাতির গাছের সংখ্যা, বিপন্ন হচ্ছে সুন্দরবনের সামুদ্রিক প্রাণ।
বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি সমস্যাকে আরও ভয়াবহ করেছে। ভূউষ্ণায়নের কারণে সমুদ্র জলের উষ্ণতা ও অম্লতা বাড়ছে। মেরুপ্রদেশ ও হিমালয়ের বরফের চাদর অতি দ্রুত গলে যাওয়ায় সমুদ্র জলের উচ্চতাও বাড়ছে, বাড়ছে জলোচ্ছ্বাস। বঙ্গোপসাগরের জলের তাপমাত্রা ২৬.৫ ডিগ্রি ও বায়ুচাপ ২০০ মিলিবারের উপরে থাকায় বাড়ছে দানবীয় সব ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও তীব্রতা। আম্ফান-ফণী-আয়লা ও ২০২১ সালের যশ ঝড়ের দগদগে ঘা এখনো শুকিয়ে যায়নি সুন্দরবনের মানুষের শরীর ও মন থেকে। IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)-এর ষষ্ঠ রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে –ভূউষ্ণায়ন ও জলবায়ুর দ্রুতপরিবর্তনের হাত ধরে আগামী দিনে প্রলয়ঙ্করী এইসব দুর্যোগের পরিমাণ বাড়বে অনেক বেশি বেশি করে। পৃথিবীর অনেক দেশের বড় বড় শহর সহ ঢাকা, কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই, বিশাখাপত্তনম, কোচি ২০৩০ সালের কাছাকাছি জলপ্লাবনে ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দুই বাংলার সমগ্র সুন্দরবনসহ বৃহত্তর কলকাতা, দমদম, ব্যারাকপুর পর্যন্ত জলের তলায় তলিয়ে। তাই সুন্দরবনকে তার নিজস্বতায় রক্ষা করতে না পারলে কলকাতা সহ দুই বাংলার প্রাণ প্রজাতির বিপর্যয় বিলুপ্তি সময়ের অপেক্ষা মাত্র।ঊ
উত্তরবঙ্গ জুড়েই হাতি ও চিতার সাথে মানুষের নিত্য সংঘাত লেগেই রয়েছে। বন্যপ্রাণীর দ্বারা মানুষের উপর আক্রমণ, হত্যা, কৃষি ফসলের ক্ষতির খবরের দিকে আমাদের চোখ চলে যায় সহজেই। যেটা আড়ালে চলে যায়, সেটা হল: ওদের বাসস্থান ও খাদ্যের ভান্ডার নষ্ট করছি আমরাই, বাধ্য হয়েই বন্যপ্রাণ চলে আসছে লোকালয়ে খাদ্যের আশায়। ফলত: সংঘাত অনিবার্য। ছুটন্ত ট্রেনের ধাক্কায় গর্ভবতী ও শিশু হাতিদের মৃত্যুর খবর আসছে নিয়মিত ভাবে। কিন্তু খবরগুলো এমনভাবে পরিবেশিত হয় যেন হাতিও পাল্টা লড়াই জারি রেখেছে। বোঝা কি এতই কঠিন যে, কাঠ পাচার বা পশু শিকারের উদ্দ্যেশ্যে বন্য জন্তুর এলাকায় ঢুকে পড়া মানুষের সঙ্গ তাদের বিরক্ত করছে, উত্যক্ত করছে তাদের? আর মুষ্টিমেয় মানুষের সুখ আরামের স্বার্থে উন্নয়নের অজুহাতে চলছে একের পর এক জঙ্গল নিধন। ওরা থাকবে কোথায়, খাবেটা কী: এই প্রশ্ন তো আমাদের বিচলিত করে না। জঙ্গলে শুধু খাবার থাকলেই তো হয় না। হাতির প্রতিদিন ঘুরে বেড়ানো, খেলা, ঘর সংসারের জন্য সারা বছর আনুমানিক ৩০০ থেকে ৫০০ বর্গ কিলোমিটার অরণ্য জরুরী। বনকে নিজের এলাকা মনে করে নির্দিষ্ট কতগুলি পথ দিয়েই হাতিরা বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াত করত স্বচ্ছন্দে, যেগুলোকে বলা হয় এলিফ্যান্ট করিডোর। অথচ দুরন্ত গতিতে ট্রেন ছুটে চলেছে করিডর নষ্ট করে। ১০০% করিডরের মুখ আগলে চাষাবাদের কাজ চলছে। হাতি চলাচলের পথের পাশ দিয়ে চা বাগান, রেললাইন, খনিজ সন্ধান, বোল্ডার সংগ্রহ এবং অধুনা মাখনমসৃণ জাতীয় সড়ক। এসবের ফলশ্রুতিতে হাতি মৃত্যুর পরিসংখ্যানটা বেশ ভয়াবহ।
একইভাবে গত তিন বছরে শুধুমাত্র কর্শিয়াং ডিভিশনেই গাড়ি চাপা পড়ে দশটি চিতাবাঘের মৃত্যু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চা বাগানের ঝোপেই আশ্রয় নেয় চিতাবাঘ। সন্তানের জন্ম দেয় তারা। চা গাছের ঝোপ তার কাছে অরণ্যের সম্প্রসারিত এক বাসস্থান বই অন্য কিছু নয়। চিতাবাঘ সংরক্ষণযোগ্য প্রাণী হিসেবে তালিকাভুক্ত হলেও মাঝেমধ্যেই কাগজের প্রথম পাতায় আমরা দেখতে পাই: নখ জিভ উপড়ে পিটিয়ে মারা, চা বাগানে বিষ দেওয়া, ফাঁদ পেতে মেরে ফেরার নিত্যনৈমিত্তিক চলচ্ছবি।
বন্যপ্রাণের বিপর্যয় আরও গভীর হল কিছুদিন আগে পাশ করিয়ে নেওয়া বন সংশোধনী আইনের মধ্য দিয়ে। এখন থেকে এই আইন মোতাবেক বনের ভিতর সরকারি, আধা সরকারিভাবে ইকোট্যুরিজম, সাফারি পার্ক, চিড়িয়াখানা করা যাবে। ফরেস্টি ওয়ার্কসের মধ্যে বনের ভিতর জরিপ, অনুসন্ধান মান্যতা পাবে। আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা থেকে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বনকে সংরক্ষণের বাইরে রাখা হবে। স্বভাবতঃই অসংরক্ষিত বনাঞ্চলে বৃহৎ বন্যপ্রাণদের বিপর্যয় বাড়বে, এমনকি তাদের বিলুপ্তিও শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। পরিবেশ আইনের পরিবর্তন কেন করছেন রাষ্ট্রনায়ক, নীতিনির্ধারকরা, তা অতি স্পষ্ট। জল জঙ্গলের দখল যেন তেন প্রকারেন দরকার কর্পোরেটের শুভাকাঙ্ক্ষীদের।
কিন্তু আমরাই বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শৈশব থেকে সচেতনতার পাঠ দিতে পারছি না কেন? আসলে গাছেরও প্রাণ আছে বা একটি গাছ অনেক প্রাণ: এইসব গালভরা কথাবার্তা লেখা থাকে পাঠ্যপুস্তকের দুই মলাটের মধ্যে, যা মুখস্ত করে পরীক্ষায় পাশ করা ছাড়া অন্য কাজে লাগে না। এই অচলায়তনের শিক্ষাব্যবস্থায় অপরিচয় এবং হাতে-কলমে না দেখার ফলে, মানুষ ভিন্ন অন্যপ্রাণকে আদতে জীবিত বলে মনে করা হয় না। যে স্কুলপড়ুয়া তার সহপাঠীকে, ভাই-বোনকে যত্ন করে, রক্ষা করার চেষ্টা করে, সেই আবার সঠিক জ্ঞানের অভাবে একটি বিষহীন সাপকেও মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। আর বয়স বাড়লে অরণ্য ভ্রমণে গিয়ে পথের দুপাশে কাচের, প্লাস্টিকের বোতল, চিপস বিস্কুট চানাচুর চকলেটের প্যাকেট ফেলে আসতে দ্বিধা করে না। কারণ অরণ্যের হস্তিটি তার কাছে ক্ষনিকের উপভোগের বস্তু। ভাগ্যক্রমে দেখে ফেলা চিতাবাঘটি সোশ্যাল মিডিয়ায় তার স্ট্যাটাস সিম্বল মাত্র। সে মনে করে, পৃথিবীটা শুধুমাত্র তার একার।
জনতত্ত্ববিদরা জানাচ্ছেন পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৮০০ কোটি, ২০৫০ সালে এটি হবে ৯৮০ কোটি। পৃথিবীতে জনসংখ্যা যত বাড়বে, তত বেশি করে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন হবে। এখানেই প্রশ্ন ওঠে সীমাহীন সম্পদ ভোগের ও ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারের অবৈজ্ঞানিক ধারণাটি নিয়ে। পৃথিবীর সবাই যদি আমেরিকার ৩৩.৬ কোটি মানুষের মতো নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করতে চায়, তাহলে মানুষের মোট পাঁচটি পৃথিবীর দরকার হবে। তাই পৃথিবীতে কীটপতঙ্গ, অনুজীব, বৃহৎ প্রাণ, উদ্ভিদ সহ মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করা। উন্নয়ন নগরায়ন খনিজ-সহ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন এবং অসীম ভোগবাদের কানাগলিতে সোনার হরিণের পিছনে ছুটলে কেবলই বিপদ বাড়বে।