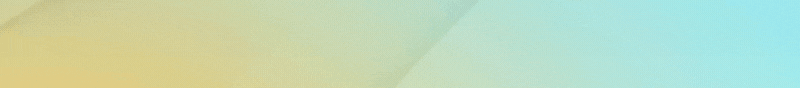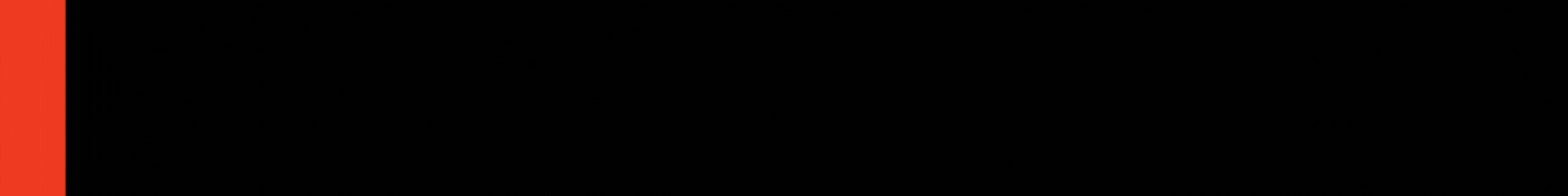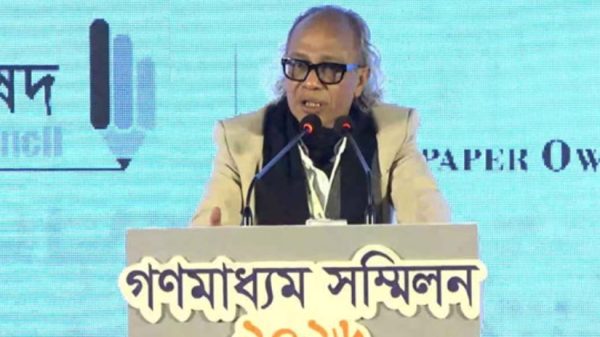সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উপকূলের মানুষ
- প্রকাশিত: রবিবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২৫
- ১২৯ বার পড়া হয়েছে

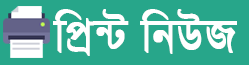
বিশেষ প্রতিনিধি : ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক/বাঁধ মেরামত করছেন বাংলাদেশের উপকূলীয় বাসিন্দারা। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সম্প্রতি এক গবেষণায় উঠে এসেছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। এই কারণে বিশেষ করে, এসব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে উদ্বেগ, হতাশা, মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তার মতো বিষয়গুলো বেড়ে গেছে।
নেচার জার্নালে প্রকাশিত ‘সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য বর্ষা–পরবর্তী মৌসুমে আরও অবনতি ঘটেছে’ শীর্ষক একটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার ১ হাজার ১৪৪ জন ব্যক্তির ওপর গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।
গবেষণায় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বিশ্বের উপকূলীয় বাসিন্দাদের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। ১৯৯০–এর দশকে বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা গড়ে আড়াই মিলিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সম্প্রতি এই হার প্রায় ৩ দশমিক ৪ মিলিমিটার। জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান গতি বজায় থাকলে, ২১০০ সালের মধ্যে এই হার বেড়ে ২৬ থেকে ৭৭ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এই পরিস্থিতি বিশ্বের প্রায় ৬০ কোটি মানুষের জীবনে ঝুঁকি তৈরি করছে। বিশেষ করে যারা উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করে, তাদের এই ঝুঁকি বেশি। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বেশ কয়েকটি পরিবেশগত সমস্যার জন্ম দেয়, যেমন: উপকূলীয় বন্যা, কৃষির ক্ষতি এবং লোকালয়ে লবণাক্ত পানি প্রবেশ—এই বিষয়গুলো জনস্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং দৈনন্দিন জীবনে বিঘ্ন ঘটায়।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি উপকূলীয় অঞ্চলে বাসিন্দাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। তবে, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি এবং ঋতুভিত্তিক প্রভাব নিয়ে গবেষণা খুব একটা হয়নি।’
এই গবেষণায় গবেষকেরা, ২০২১ সালের মার্চ থেকে এপ্রিল (বর্ষা মৌসুমের আগের মাসগুলো) এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর (বর্ষা–পরবর্তী মৌসুম) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব অনুসন্ধান করেন। ১ হাজার ১৪৪ জন অংশগ্রহণকারীর ওপর পরিচালিত দীর্ঘমেয়াদি এই গবেষণায় তাঁরা মানসিক স্বাস্থ্যে বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।
বিশেষ করে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি কীভাবে উপকূলীয় মানুষের মধ্যে উদ্বেগ, হতাশা, মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা বাড়ায় সে বিষয়ে তাঁরা গবেষণা করেছেন। এ ছাড়া, পরিবেশগত উপাদান এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিও পরিমাপ করা হয়েছে এই গবেষণায়।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘ফলাফল থেকে জানা গেছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপক অবনতি ঘটে। বিশেষত বর্ষা-পরবর্তী সময়ে দুশ্চিন্তা, হতাশা, উদ্বেগ ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়। বেশি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মানসিক অস্থিরতা বর্ষা-পরবর্তী সময়ে আরও বাড়ে। পরিবেশগত চাপ এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ করে মাঝারি ও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বর্ষা-পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধি পায়। আমাদের এই গবেষণার ফলাফল দেখায়, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো দূর করতে তাৎক্ষণিক সহায়তা এবং স্থিতিশীলতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।
বাংলাদেশের দক্ষিণ-মধ্য উপকূলের চর গঙ্গামতীর বাসিন্দা মোহাম্মদ তানজিদ বলেন, গত পাঁচ বছরে ব্যাপক ভাঙ্গনের ফলে বিস্তীর্ন এলাকা সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে গেছে ।
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকরা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তনশীল সমুদ্র উপকূলরেখা, অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারনে বিশাল এক জনগোষ্ঠির জীবিকাকে এখন হুমকির মুখে।
মাখেন রাখাইন (৩৫) একজন আদিবাসী কৃষক। বসবাস করেন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীর উপজেলায়। সরেজমিনে রাঙ্গাবালীতে পরিদর্শনের সময় দ্য থার্ড পোলের সাথে কথা হয় মাখেন রাখাইনের। তিনি বলেন, “২০২২ সালে আমি মসুর ডালে বীজ বপন করেছিলাম, কিন্তু গত চৈত্র মাসে (বাংলা বছরের শেষ মাস) অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের কারনে আমার ফসলের জমি মারাত্বক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমি জমি থেকে বলতে গেলে ফসল তুলতেই পারিনি। অথচ আমাদের এখানে চৈত্র মাসই ছিল মসুর চাষের মূল মৌসুম’।
ভালো মুনাফার আশায় ইজারা নিয়ে এক একর জমিতে মসুরের চাষ করেন মাখেন রাখাইন। কিন্তু ২০২৩ সালের মার্চ এবং এপ্রিলের শুষ্ক মৌসুমেও অস্বাভাবিক ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে তার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এর আগে কোনো শুষ্ক মৌসুমেই পটুয়াখালী জেলায় এতটা বৃষ্টি পাত দেখা যায়নি কখনো। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, ঘন ঘন বৃষ্টিপাত কৃষকদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তারা কেবল ফসলের ধরণ পরিবর্তন করতেই বাধ্য হয়নি বরং ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং জলোচ্ছ্বাসের কারনে একত্রে এই জেলার কৃষি উৎপাদন মারাত্বকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।
এই প্রতিবেদকের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে মাখেন রাখাইন ফসলের জমিতে কীটপতঙ্গের আক্রমন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, “আজকাল জমিতে পােকামাকরের আক্রমনের ধরণে বেশ পরিবর্তন এসেছে। প্রচলিত কীটনাশক ব্যবহার করেও জমিতে এদের আক্রমন বন্ধ করা যাচ্ছে না। ফলে জমিতে ফসলের অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।
রাঙ্গাবালীর উপজেলায় আদিবাসী কৃষক মাখেন রাখাইন এক একর জমি ইজারা নিয়ে মসুরের চাষ করেন। কিন্তু ২০২২ সালে শুষ্ক মৌসুমে অপ্রত্যাশিত বৃষ্টির কারনে তার ফসল নষ্ট হয় যায়। সারা বছরের খাদ্যের যোগান দিতে তাকে এখন ধানের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। (ছবি: রফিকুল ইসলাম/দ্য থার্ড পোল)
জমিতে কীটপতঙ্গের আক্রমনকে একটি মারাত্বক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন কৃষকরা। তাদের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ফসলের জমিতে পোকামাকরের আক্রমন বেড়ে যাচ্ছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় রাসায়নিক কীটনাশকের পেছনে তাদের এখন অনেক বেশি খরচ করতে হচ্ছে
মাখেন রাখাইন বলেন, কৃষকরা এরইমধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে আর্থিক সংকটের সাথে লড়াই করে যাচ্ছে। একইসঙ্গে এখন কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং বেশি পরিমাণে সার ব্যবহারের কারণে ফসল উৎপাদনে স্বাভাবিকের চেয়ে ব্যয় আরো অনেক বেশি হবে।
রাঙ্গাবালির কৃষক সালমা বেগমও (৪০) একই ধারনার কথা বলেন। ২০২২ সালে জমিতে রোপণ করা সালমা বেগমের ধান এবং মসুর ডালের ফসল কীটপতঙ্গ এবং বৃষ্টিতে মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
২০২২ সালের প্রকাশিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রকৃতিতে চরম আবহাওয়া এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে ধানের ফসলে পোকামাকরের আক্রমণ বেড়েছে। এরসঙ্গে জমিতে অত্যধিক লবণাক্ততার প্রভাব মেটাতে কৃষকরা প্রতি বছর ধান ক্ষেতে সারের পরিমাণের প্রয়ােগ বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে, যার ফলে তাদের জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ নষ্ট হচ্ছে।
রাঙ্গাবালীর মওদুদী ইউনিয়নের স্থানীয় চেয়ারম্যান মাহমুদ হাসান বলেন, উপকূলীয় অঞ্চলে এখন বর্ষাকালে সামগ্রিকভাবে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং শুষ্ক মৌসুমে অতিরিক্ত খরা দেখা যাচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টিপাত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত না থাকলেও অতিরিক্ত বৃষ্টির কারনে ফসলের খুব ক্ষতি হয়। আবার এসব উপকূলীয় এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে সুপেয় পানির অভাবের কারনে খরার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
“কৃষকরা এ বছর দুইবার আমনের [দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ ধানের জাত] চারা বুনতে বাধ্য হয়, [এ ধরনের ঘটনা এবারই প্রথম] । এর কারন অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণেপ্রথমবার ধানের চারা নষ্ট হয়ে যায়। আবার শুষ্ক মৌসুমে ডাল এবং তরমুজের চাষ সহজ হলেও বিশুদ্ধ পানির অভাবের এর ফলন মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়।”
তিনি আরো বলেন, শীতকালে কম বৃষ্টিপাতের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর মারাত্মকভাবে নিচে নেমে যায় এবং সে কারণে কৃষকরা তাদের ক্ষেতে সেচের জন্য কৃত্রিম পানির উৎস স্থাপনের জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয়।
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু বিপর্যয় যেমন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং জলোচ্ছ্বাস এবং লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। প্রায় প্রতি বছরই গ্রীষ্মে ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা লক্ষ লক্ষ উপকূলীয় মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যার ফলে প্রাণহানি এবং সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়।
হানিফ পন্ডিত একজন জেলে। সারা জীবন মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহকারী এই জেলে বলেন তিনি এখন সাগরের রুক্ষ বাতাস এবং অপ্রত্যাশিত আবহাওয়ার ধরণ বুঝে উঠার চেষ্টা করছেন
রাঙ্গাবালির জাহাজমারায় বসবাসকারী ৬০ বছর বয়সী জেলে হানিফ পণ্ডিত। ছোটবেলা থেকেই তিনি বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরছেন। দ্য থার্ড পোলকে তিনি বলেন, “ঘূর্ণিঝড় এবং ঝড়ো আবহাওয়া উপকূলীয় জেলেদের ভীষন প্রভাবিত করে।” তিনি বলেন, “কয়েকদিন আগে প্রবল বাতাসের কবলে পড়ে মাছ ধরার নৌকা থেকে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি পরে তীরে পৌঁছেছিলাম অন্য একটি নৌকার সাহায্যে। ”
পটুয়াখালীর চর গঙ্গামতীর বাসিন্দা শাহিন বেপারীর বক্তব্য ও একই ধরনের। তিনি বলেন, সাগরে বাতাস তীব্র হয়ে উঠেছে এবং মাছ ধরার নৌকা “অনেকবার প্রবল বাতাসে উল্টে গেছে, আর এর ফলে জেলেদের নীয়মিত জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে।”
দেশের ৫৮০ কিলোমিটার-বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যা সেখানে বসবাসকারী জনগণকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। ২০২২ সালের বিশ্বব্যাংকের একটি সমীক্ষায় বলা হয় দেশের ৪ মিলিয়ন মানুষ ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ৩ মিটারের বেশি গভীরতায় প্লাবিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এতে আরো বলা হয় আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ১৩.৫ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে।
মৌডুবি ইউনিয়নের ভূঁইয়া কান্দার জেলে রাকিব হোসেন (৪০) বলেন, তারা প্রতিবছর উপকূলীয় এলাকার বন্যার সম্মুখীন হয়। রাকিব হোসেন বলেন, একবার বন্যা উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানলে মাছ ধরার জাল ভেসে যায়। আর তার ফলে তাদের একমাত্র জীবিকা হুমকির মুখে পড়ে।
পরিবর্তিত আবহাওয়ার কারণে সাগরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না থাকায় মাছ ধরতে যেতে পারেননি রাকিব। ফলে প্রায় তিন মাস তাকে বাড়িতে বেকার হয়ে বসে থাকতে হয় ।
তিনি বলেন, “এখন আমরা প্রতিকূল আবহাওয়ায় সমুদ্র থেকে পর্যাপ্ত মাছ ধরতে পারছি না। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার কারণে বছরে প্রায় দুই মাস আমাদের মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হয়। এই সময়ে [এপ্রিল/মে মাসে গ্রীষ্মের শুরুতে এবং অক্টোবর/নভেম্বরের শেষের বর্ষাকালে], আমাদের সংসারের ব্যয় মেটাতে খুব কষ্ট হয়।“
বিশিষ্ট পানি বিশেষজ্ঞ ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সুপার সাইক্লোন হবে যার ঢেউয়ের উচ্চতা ১৬ ফুট বা প্রায় ৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এগুলো বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানতে পারে। আমাদের এই ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।”
উপকূলীয় বাংলাদেশে বসবাসকারী মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল পরিবর্তশীল উপকূলরেখা। বাংলাদেশের উপকূল থেকে মাত্র একশ কিলোমিটার উজানে চীন, ভারত, নেপাল আর ভূটান থেকে প্রবাহিত নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা একসাথে মিলিত হয়ে একটি অববাহিকা সৃষ্টি করেছে। হিমালয় পর্বত থেকে প্রবাহিত এই নদীগুলি প্রচুর পরিমাণে পলি বহন করে। ২০২১ সালে সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)-এর একটি সমীক্ষার ফলাফল বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে বলা হয় গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদী সব মিলিয়ে প্রায় এক ট্রিলিয়ন ঘনমিটার পানি প্রবাহের মাধ্যে বঙ্গোপসাগরে বছরে প্রায় এক বিলিয়ন টন পলি বহন করে নিয়ে যায়।
“গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনাসহ অনেক বড় আন্তঃসীমান্ত নদী রয়েছে, যেগুলো প্রচুর পরিমাণে পলি বহন করে এবং এটি মেঘনা মোহনায় গিয়ে জমা হয়। এর ফলে উপকূলে সীমারেখা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়।” সিইজিআইএস-এর সিনিয়র উপদেষ্টা মমিনুল হক সরকার দ্য থার্ড পোলকে এ তথ্য জানান।
হিমালয়সৃষ্ট নদী দ্বারা বাহিত বিপুল পরিমাণ পলি বাংলাদেশের উপকূলরেখার কিছু অংশ ধীরে ধীরে প্রসারিত করেছে ।
স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে ২০২০ সালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়, পলির এই বার্ষিক প্রবাহের কারণে, উপকূলীয় অঞ্চলে ১৯৮৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ভূমির আয়তনে ১.১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সব মিলে ৫৯১ বর্গ কিলোমিটারের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা ২৮,৮৩৬ বর্গ কিলোমিটার (দেশের মোট ভূমির ৫৬.০৬%) থেকে ২০১৮ সালে ২৯,৪২৭ বর্গ কিলোমিটার (৫৭.২১%) বেড়েছে।
গবেষণার সহ-লেখক কবির উদ্দিন এই প্রতিবেদককে বলেন, “বাংলাদেশ যেহেতু হিমালয়ের নদীগুলো থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ পলিমাটি পায়, তাই এর ভূমির আয়তন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।”
সমীক্ষাটি আরো বলা হয়, “উত্তর বঙ্গোপসাগর জুড়ে বাস্তুতন্ত্র এবং তাদের পরিষেবাগুলোর পুনর্বাসন, পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা” এর জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।”
ভূমি সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে ভাঙ্গনের ফলে ক্রমাগত উপকূলরেখা হারিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালের একটি উপকূলীয় ক্ষয়জনিত দুর্বলতা মূল্যায়ন অনুসারে, উপকূলীয় ভাঙ্গনের ফলে প্রায় ১১% উপকূলরেখা খুব উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে, যেখানে “উচ্চ ঝুঁকির” অঞ্চলগুলি ২৪%। সম্প্রতি পটুয়াখালীর কুয়াকাটা পরিদর্শনকালে দ্য থার্ড পোল দেখেছে যে এলাকার উপকূলরেখার ৭ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ভাঙনের ফলে সেখানকার বাসিন্দাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, হোটেল, সংরক্ষিত বন, বসতবাড়ি এবং পার্ক সাগর গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।
কয়েক বছর আগেও কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের কাছেই দেখা যেত কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান। আজ অবশ্য এর প্রবেশপথের মাত্র দুটি স্তম্ভ দৃশ্যমান। এর দুই-তৃতীয়াংশই সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে গেছে।
পটুয়াখালী বন বিভাগের একজন স্থানীয় বনরক্ষী এই প্রতিবেদককে বলেছেন, অতিরিক্ত ৪০ হেক্টর বনভূমি প্রতি বছর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির বিপুল সংখ্যক গাছ মারা যায় এবং উপড়ে যায়। এতে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত গঙ্গামতি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে।
কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের সারি সারি মৃত গাছ, যা গত দুই দশক ধরে ধীরে ধীরে উচ্ছেদ হয়েছে। পুরো সৈকত জুগে এখন উপড়ে পড়া ক্ষতিগ্রস্ত গাছের সারি।
কুয়াকাটার চর গঙ্গামতির বাসিন্দা মোহাম্মদ তানজিদ বলেন, ভাঙন তাদের এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। তিনি বলেন, “গত পাঁচ বছরে কুয়াকাটা উপকূলের প্রায় ২৫০ মিটার জমি সমুদ্রের পানির নিচে চলে গেছে।”
জলবায়ু প্রভাব আর সেইসাথে মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে প্রকৃতিতে এধরনের পরিবর্তন দৃশ্যমান হচ্ছে। হিন্দুকুশ- হিমালয়ের পানি, বরফ, সমাজ এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট (ICIMOD) এর একটি রিপোর্ট অনুসারে, ২০৫০ সালে হিমালয় অঞ্চল থেকে পানির সরবরাহ সর্বোচ্চ হবে৷ পানি হ্রাসের অর্থ হবে স্বল্প পলি বহন। একই সঙ্গে বাড়বে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। কম পলিমাটি এবং পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে উপকূলরেখা ক্রমবর্ধমান সাগরের কারনে হুমকির সম্মুখীন হবে
কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায়, “১৩৯টি পোল্ডারে ৫,৮১৬ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ [বেড়িবাঁধ দ্বারা ঘেরা জমি]” সমাধানের অংশ হিসাবে দেখা হয়, যদিও উল্লেখ করা হয়েছে যে বিদ্যমান সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১৮% বৃদ্ধি পাবে।
সরকার বাঁধ এবং জিওব্যাগ (বালি বোঝাই পাটের ব্যাগ) দিযে পানি আটকাতে বাঁধ তৈরির চেষ্টা করছে। কিন্তু উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এগুলি দ্রুতই অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে ।
২০২৪ সালের জুন মাসে তৎকালীন পরিবেশমন্ত্রী মো বাংলাদেশ সংসদে বলেন, এই শতকের শেষ নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে দেশের ১২- ১৮ % বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে। তা সত্ত্বেও, দেশটি স্বল্পমেয়াদী সমাধানের পথকেই বেছে নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে যা পলির আধিক্য কমিয়ে এনে চলমান সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে।
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (বিডব্লিউডিবি) মহাপরিচালক এসএম শহিদুল ইসলাম দ্য থার্ড পোলকে বলেন, বঙ্গোপসাগরে জমা পলি ব্যবহার করে সমুদ্র থেকে ভূমি পুনরুদ্ধার করার জন্য বাংলাদেশ একটি মেগা প্রকল্প শুরু করলে প্রকৃতপক্ষে ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হবে।
তিনি বলেন, উপকূলীয় ভাঙ্গন মোকাবেলায় বিডব্লিউডিবি উপকূলরেখা বরাবর ভাঙনপ্রবণ এলাকায় জিওব্যাগ স্থাপন করছে এবং পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ভোলা, বরগুনা ও বাগেরহাটে এবংখুলনা সাতক্ষীরা ঘূর্ণিঝড়, উপকূলীয় বন্যার সময় স্থানীয় জনগণ ও তাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য উপকূলীয় বেড়িবাঁধ উঁচু করছে।