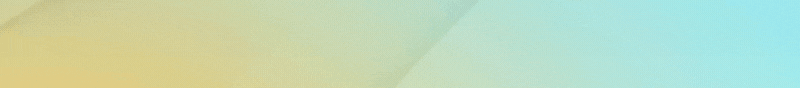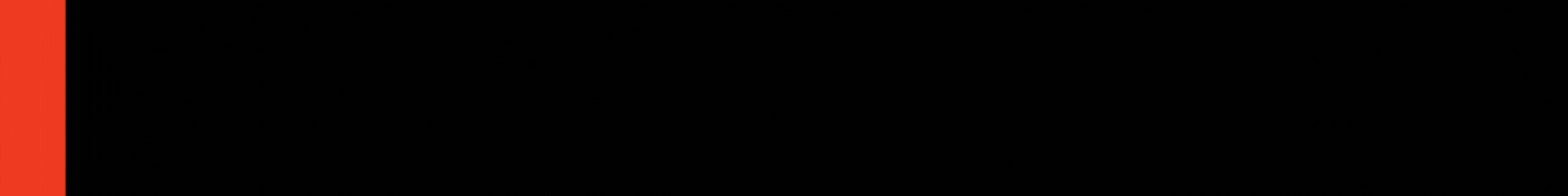শনিবার, ১৭ জানুয়ারী ২০২৬, ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
৯ মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে দেশ, প্রস্তুতির ব্যবস্থা আছে কি?
- প্রকাশিত: শনিবার, ২২ নভেম্বর, ২০২৫
- ১০০ বার পড়া হয়েছে

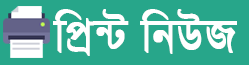
- বিশেষ প্রতিনিধি : শুক্রবার সকালে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার পর দেশজুড়ে যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে, তার মধ্যেই বিশেষজ্ঞরা এক ভয়াবহ সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তারা বলছেন, বাংলাদেশ যেকোনো সময় ৯ মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে।
- ইতোমধ্যে এই ভূমিকম্পে বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন এবং ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ভবনে ফাটল ধরেছে বলে জানা গেছে।
- ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ সৈয়দ হুমায়ুন আখতার একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই ঝুঁকির বিষয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, ২০০৩ সাল থেকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তারা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- যেহেতু বাংলাদেশ তিনটি প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত, তাই প্লেটগুলোর ত্রিমাত্রিক গতি নির্ণয়ের জন্য জিপিএস স্থাপন করা হয়। ১৪ বছরের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্লেটের গতির পরিমাপ নির্ণয় করে তারা ২০১৬ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।সেই প্রতিবেদনে দেখা গেছে, সিলেট থেকে কক্সবাজার অঞ্চলে ৮ দশমিক ২ থেকে ৯ মাত্রার শক্তিসম্পন্ন ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার মতো বিপুল শক্তি প্লেটে জমা হয়ে আছে।
- বিশেষজ্ঞ আখতার বলেন, এই শক্তি যেকোনো সময় বের হয়ে আসতে পারে। এই শক্তি একবারে বের হতে পারে আবার ধীরে ধীরেও বের হতে পারে। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন সাবডাকশন জোনে হওয়া ভূমিকম্পগুলো থেকে সাধারণত ৬৫ থেকে ৮০ ভাগ শক্তি একবারে বের হয়েছে এবং বাকিটা ধীরে ধীরে বের হতে থাকে। একই রকম পরিস্থিতি বর্তমানে বাংলাদেশে বিরাজ করছে।তিনি উল্লেখ করেন, প্রায় ৮০০ থেকে এক হাজার বছর আগে কুমিল্লার ময়নামতিতে এক ভূমিকম্পের মাধ্যমে প্লেটগুলো তাদের জমাট বাঁধা শক্তি বের করেছিল।
- এরপরই নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে এই অবস্থায় এসেছে। তার মানে, গত এক হাজার বছর ধরে শক্তি জমা হতে হতে ৮.২ থেকে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার মতো শক্তি এখন জমা হয়েছে। গত বছর থেকে এখন পর্যন্ত সিলেট, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জসহ দেশের বেশ কয়েকটি স্থানে যে ভূমিকম্পগুলো হয়েছে, সেগুলো এই সাবডাকশন জোনের মধ্যে ঘটেছে। বিশেষজ্ঞের মতে, এগুলোই বড় ভূমিকম্প হওয়ার আলামত। তিনি সতর্ক করে বলেন, বড় ভূমিকম্প আজ হতে পারে, কালও হতে পারে, আবার ৫০ বছর পরেও হতে পারে।
- মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের মতো বাংলাদেশেও শক্তিশালী ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ শক্তিশালী ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। শনিবার ফায়ার সার্ভিসের সদরদপ্তরের মিডিয়া সেলে থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
- ফায়ার সার্ভিস জানায়, মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে পর পর দুইটি শক্তিশালী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প দুইটির মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৭.৭ ও ৬.৪। ফলে ওই দেশ দুটি বেশ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশেও একই মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা অঞ্চল উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
- এমতাবস্থায় ভূমিকম্প মোকাবিলার জন্য সকল পর্যায়ে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ ও সচেতনতা তৈরির নিমিত্তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর নি¤œরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করছে। এগুলো জচ্ছে-বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০২০ অনুযায়ী ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন নির্মাণ করা। ঝুঁকিপূর্ণ ও পুরোনো ভবনগুলোর সংস্কার ও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সকল বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনে অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা। ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহ যথা গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের লাইনের সঠিকতা নিশ্চিত করা। ভূমিকম্প চলাকালীন সময়ে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পর্যায়ে বিভিন্ন করণীয় সম্পর্কে নিয়মিত মহড়া অনুশীলন ও প্রচারের ব্যবস্থা করা। জরুরি টেলিফোন নম্বর যেমন ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, হাসাপাতাল ও অন্যান্য জরুরি নম্বরসমূহ ব্যক্তিগত পর্যায়ের পাশাপাশি সকল ভবন বা স্থাপনায় সংরক্ষণ করা এবং তা দৃশ্যমান স্থানে লিখে রাখা।
- ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দুর্যোগকালীন সময়ে কার্যকর ভূমিকা রাখা। জরুরি প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সরঞ্জামাদি যেমন- টর্চলাইট, রেডিও (অতিরিক্ত ব্যাটারিসহ), বাঁশি, হ্যামার, হেলমেট/কুশন, শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি, প্রয়োজনীয় ঔষধ সামগ্রী, ফার্স্ট এইড বক্স, শিশু যতেœর সামগ্রী ইত্যাদি বাসা-বাড়িতে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা যাতে ভূমিকম্প পরবর্তীতে আটকা পরলে তা ব্যবহার করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা যায়। সকল পর্যায়ে তদারকি সংস্থার কার্যক্রমে সহযোগিতা করা। উপরোক্ত বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রেখেছে। আসুন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সতর্কতায় ভূমিকম্পের ন্যায় ভয়াবহ দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা সীমিত রাখি।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন্স অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, সবার আগে ভূমিকম্পে সচেতনতা জরুরি। ঢাকা শহরের বেশিরভাগ ভবন ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য ভবনগুলো ভূমিকম্প নিরোধক কিংবা মজবুত করা প্রয়োজন। ‘৭ মাত্রার ভূমিকম্প যদি সীমান্ত এলাকায় হয় তাহলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে বাংলাদেশকে। বিশেষ করে ময়মনসিংহ, রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ক্ষয়ক্ষতি হবে। ঢাকায় ক্ষয়ক্ষতি হবে কারণ ঢাকার ভবনগুলো বেশিরভাগ ঝুঁকিপূর্ণ।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান বলেন, ভূমিকম্পে বাংলাদেশও কেঁপে উঠেছে। এগুলো ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল, কারণ প্লেট বাউন্ডারি। প্লেট বাউন্ডারি বরাবর এরকম প্রতিদিনই প্রচুর হয়, যেগুলো ছোটো ছোটো ভূমিকম্প, তবে মাঝেমধ্যে বড় ভূমিকম্পও হয়। ৭ মাত্রার ভূমিকম্প যদি সীমান্ত এলাকায় হয় তাহলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে বাংলাদেশকে। বিশেষ করে ময়মনসিংহ, রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ক্ষয়ক্ষতি হবে। ঢাকায় ক্ষয়ক্ষতি হবে কারণ ঢাকার ভবনগুলো বেশিরভাগ ঝুঁকিপূর্ণ।
- তিনি বলেন, বাংলাদেশ প্লেট বাউন্ডারির কাছাকাছি আছে, আগেও এখানে বড় ভূমিকম্প হয়েছে এবং আগামীতেও হতে পারে। ঝুঁকির দিক থেকে বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকিপ্রবণ দেশ। সেই ঝুঁকি অনুযায়ী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভবনের নকশা করা নেই। পুরাতন ভবনগুলো নাজুক এবং নতুন ভবনগুলো গ্রাউন্ড প্যারামিটার অনুযায়ী করা হয়নি। এ কারণে ঝুঁকি অনেক বেশি। ভূমিকম্প সহায়ক ভবন বাংলাদেশেও করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্র, জাপানসহ উন্নত দেশগুলো করেছে।
- কানাডার সাসকাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে আবহাওয়া ও জলবায়ুবিষয়ক পিএইডি গবেষক এবং আবহাওয়াবিদ মোস্তফা কামাল পলাশ জানিয়েছেন, গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের পাশে এত শক্তিশালী ভূমিকম্প সংগঠিত হয়নি। শুক্রবার মিয়ানমারের ভূমিকম্পটি খুবই শক্তিশালী ছিল। এই ভূমিকম্পের তিন ঘণ্টার মধ্যে চারটি আফটার শক হয়েছে। এর মধ্যে যথাক্রমে ভূমিকম্পের মান ছিল ৬ দশমিক ৬, দুটি ৪ দশমিক ৬ ও একটি ২ দশমিক ৮ মাত্রার।
- বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য যত ভূমিকম্প: বাংলাদেশে গত মে মাস থেকে ছোট ও মাঝারি বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প হয়েছে। এসব ভূমিকম্পের উৎপত্তি ছিলো দেশের সীমানার ভেতর অথবা আশেপাশে। ভারত ও বার্মা প্লেট এবং বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থান বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বলছেন, যে কোনো সময় দেশে বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানবে। বড় মাত্রার ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে রাজধানীসহ ঢাকা বিভাগের। ঝুঁকিতে আছে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগ।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অন্যতম শক্তিশালী ভূমিকম্প হয় ১৮২২ ও ১৮১৮ সালে। ১৮২২ সালে সিলেটে হয়েছিলো ৭ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প এবং শ্রীমঙ্গলে হয়েছিলো ৭ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প। সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ১৫৪৮, ১৬৪২, ১৬৬৩, ১৭৬২, ১৭৬৫, ১৮১২, ১৮৬৫, ১৮৬৯ সালে ভূমিকম্প হওয়ার ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এসবের মাত্রা কত ছিল তা জানা যায় না।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ড. মো. আনোয়ার হোসেন ভূঁঞা বিসিসিকে বলেন, বাংলাদেশে গত ১২০ থেকে ১২৫ বছরে মাঝারি ও বড় মাত্রার প্রায় শতাধিক ভূকম্প অনুভূত হয়েছে। তবে এসবের মধ্যে সাত বা তার চেয়ে বড় মাত্রার ভূমিকম্পের সংখ্যা খুব বেশি নয়।
- ২০২৩ সালের মে থেকে আগস্ট মাসে বাংলাদেশে ১৪ অগাস্ট রাত ৮টা ৪৯ মিনিটের দিকে একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয় রাজধানীসহ দেশের বেশিরভাগ এলাকায়। মার্কিন ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস-এর তথ্য অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পটির মাত্রা রিখটার স্কেলে ছিল ৫.৫ যা মাঝারি মাত্রার একটি ভূমিকম্প। গত ১৬ জুন রাজধানীসহ সারা দেশে ৪.৫ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্প হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেটের গোলাপগঞ্জ। ভূমিকম্পের আগে-পরে শিলংয়ে সরকারি ভবনের অবস্থা। ইমেজ- জিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া
- এপ্রিল ২৫, ২০১৫: দক্ষিণ এশিয়ার দেশ নেপালে ২০১৫ সালে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে প্রায় ৯ হাজার মানুষ নিহত হন। ওই ভূমিকম্প এতোটাই শক্তিশালী ছিল যে এটি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, ভুটান, চীনসহ আশপাশের প্রায় সব দেশে অনুভূত হয়েছিল। ৪ জানুয়ারি, ২০১৬: ২০১৬ সালের ৪ জানুয়ারি ৬ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল বাংলাদেশ। সেবার আতঙ্কেই মারা যান ছয়জন। ১৯৯৯ সালের ভূমিকম্প: বিংশ শতকে বাংলাদেশের শেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্পটি হয় মহেশখালী দ্বীপে। ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসের সেই ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল এই দ্বীপেই। ৫.২ মাত্রার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দ্বীপের অনেক বাড়িঘর। ১৯৯৭ সালের ভূমিকম্প: ১৯৯৭ সালের ২১ নভেম্বর চট্টগ্রামে ৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্প ঘটে। এতে শহরের নানান স্থাপনায় ফাটল ধরে। ১৯১৮ সালের ভূমিকম্প: ১৯১৮ সালে প্রায় ৭.৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয় শ্রীমঙ্গলে। যা শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প নামেই পরিচিত। মিয়ানমার ও ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলেও অনুভূত হয়েছিল এই ভূমিকম্প। শ্রীমঙ্গলের অনেক দালান-কোঠা ধ্বংস হয়েছিল ওই ভূকম্পনে। ১৯৫০ সালের ভূমিকম্প: ওই বছর ভারতের অরুণাচল প্রদেশে ৮.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এতে ভারতের প্রায় চার হাজারের বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছিল। কম্পন অনুভূত হয়েছিল বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং চীনের কিছু অংশে। তবে এসব এলাকায় তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এছাড়া ১৯৩৪ সালের দিকে বিহার ভূমিকম্প সংগঠিত হয় যার ক্ষতিকর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছিল।বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকিমূক্ত হবে ২০৭১ সালে: এনামবাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকিমূক্ত হবে ২০৭১ সালে: ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্প: ১৮৯৭ সালের ১২ জুন এটি শিলং প্ল্যাটুতে আঘাত হানে। এই ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৮.২। এটা গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকোয়েক নামে পরিচিত। এটার ঝাঁকুনি দিল্লি, পেশোয়ার পর্যন্ত অনুভূত হয়েছিল। এই ভূমিকম্পে মেঘালয়, সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় ১৬শ’র বেশি মানুষ মারা যায়।
- ১৮৮৯ সালের ভূমিকম্প: ১৮৮৯ সালের ১০ জানুয়ারি ওই ভূমিকম্পটি মেঘালয়ে আঘাত হানে। ভূমিকম্পটি সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এর কেন্দ্রস্থল ছিল ভারতের মেঘালয়ের জৈন্তা পাহাড়। এর মাত্রা ছিল ৭.৫। সিলেট শহর এবং আশপাশের এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়েছিল। ১৭৬২ সালের ভূমিকম্প: টেকনাফ থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত প্রায় ৪০০ কিলোমিটার জায়গায় যে ফল্ট লাইন রয়েছে সেখানে ৮.৫ মাত্রার বেশি শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়। এর ফলে সেন্টমার্টিন আইল্যান্ড তিন মিটার উপরে উঠে আসে। এর আগে সেন্টমার্টিন আইল্যান্ড ছিল ডুবন্ত দ্বীপ।
- কয়েক বছর ধরে দেশে ছোট ও মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, ঘন ঘন হালকা ভূকম্পন মূলত একটি ‘বড় শক্তির ভূমিকম্পের প্রাথমিক ধাপ’ এবং বাংলাদেশ বর্তমানে প্রায় ১৫০ বছরের যে ভূকম্পন চক্রের মধ্যে আছে, তাতে যেকোনো মুহূর্তে রিখটার স্কেলে ৮ দশমিক ২ মাত্রার মতো প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প হতে পারে।
- তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ১৫ মাসের ব্যবধানে দেশে ছোট ও মাঝারি মাত্রার প্রায় ২১টি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে হওয়া ১২টি ভূমিকম্পের মধ্যে ৩টির মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৫-এর ওপরে। সর্বশেষ আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে ৫.৫ মাত্রার এ ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীতে।
- এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে অনুভূত হওয়া ভূকম্পনগুলোর মধ্যে একটি ছিল ২০২৩ সালের ৫ মে ভোরে, যার উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার খুব কাছের উপজেলা দোহারে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪.৩ (সময়: সকাল ৫টা ৫৭ মিনিট)। এর আগে, লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে (ঢাকা থেকে ৮৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে) উৎপত্তিস্থল হওয়া অন্য একটি ভূমিকম্পের কারণে কিছু কিছু স্থানে বড় বড় ভবনে ও ঘরের ছাদে ফাটল ধরেছে, মেঝের টাইলসে ফাটল ধরেছে এবং কোথাও ভবন থেকে দ্রুত নিচে নামতে গিয়ে শতাধিক পোশাকশ্রমিকের আহত হওয়ার খবরও পাওয়া গেছে।
- ভূতত্ত্ববিদদের মতে, বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে একটি অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায়, যেখানে দুটি সক্রিয় টেকটনিক প্লেট—ভারতীয় প্লেট ও মিয়ানমার (বার্মা) টেকটনিক প্লেট—পরস্পরকে স্পর্শ করে আছে।
- এই দুটি প্লেটে সংঘর্ষের কারণেই এত ভূমিকম্প হচ্ছে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার সাহা জানান, দেশে দুই ধরনের ভূমিকম্প হচ্ছে:
- এর মূল কেন্দ্র সাধারণত দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (সিলেট) বা আসাম-শিলং প্লেটের কাছাকাছি থাকে, যার প্রভাব ঢাকাতেও পড়ে।
- এটি প্লেট বাউন্ডারি ছাড়া ফল্ট লাইনে হয়। মধুপুর ফল্টলাইন অন্যতম। এ ছাড়া ২০০১ সাল থেকে বুড়িগঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের আশপাশেও উৎপত্তিস্থল দেখা যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ২০০১ সালে বুড়িগঙ্গার কাছে, ২০০৮ সালে মানিকগঞ্জে এবং পরে চাঁদপুর ও ময়মনসিংহে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল। পদ্মা বা মেঘনার আশপাশে ফল্ট লাইন আছে কিনা, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার সতর্ক করে বলেন, এই অঞ্চলে বড় ভূমিকম্পের শক্তি বহু বছর ধরে সঞ্চিত হয়ে আছে। ইন্ডিয়া ও বার্মা প্লেটের সংযোগস্থলে প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ বছর আগে ভূমিকম্প হয়েছিল। এই শক্তি একসঙ্গে মুক্ত হলে ৮.২ মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা সৃষ্টি হবে।
বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত এক গবেষণায় দেশের ঝুঁকির ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে:
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঢাকা শহরের বহু ভবনের নির্মাণ দুর্বলতা এই ক্ষতির আশঙ্কা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নগর-পরিকল্পনাবিদ আকতার মাহমুদ জানান, ঢাকা শহরে অনেক বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে ইমারত নীতিমালা ও ভূমির ধরন না মেনে।
যেসব ভবন বালু ও নরম মাটিতে (বিশেষত জলাভূমি ভরাট করে) নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলোর ঝুঁকি অনেক বেশি। তবে যেসব ভবন লাল মাটি বা শক্ত মাটির ওপর নির্মিত, সেগুলোর ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম।
ভূমিকম্প হবে ধরে নিয়েই প্রস্তুতি নিতে এবং জাতীয় ভবন নির্মাণ নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে দালানকোঠা নির্মাণ করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।
ভূমিকম্প আগাম বার্তা দিয়ে আসে না। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় মানুষের করণীয় হলো আগাম সতর্কতা ও প্রস্তুতি নেওয়া। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বড় ঝুঁকি এড়ানোর জন্য রাজউককেই দায়িত্ব নিতে হবে ঢাকার ভবনগুলো নতুনভাবে পরীক্ষা করে ত্রুটিপূর্ণ বা ডিফল্ট ভবনগুলো ভেঙে ফেলার জন্য। পাশাপাশি, জাতীয় ভবন নির্মাণ নীতিমালা মেনে চলতে জনগণকে সতর্ক ও সচেতন করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।
আরো সংবাদ পড়ুন
© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত -২০২৫, আমাদের প্রকাশিত সংবাদ, কলাম, তথ্য, ছবি, কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ।
ওয়েবসাইট ডিজাইন : ইয়োলো হোস্ট