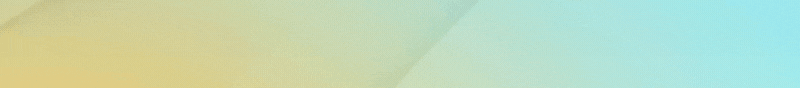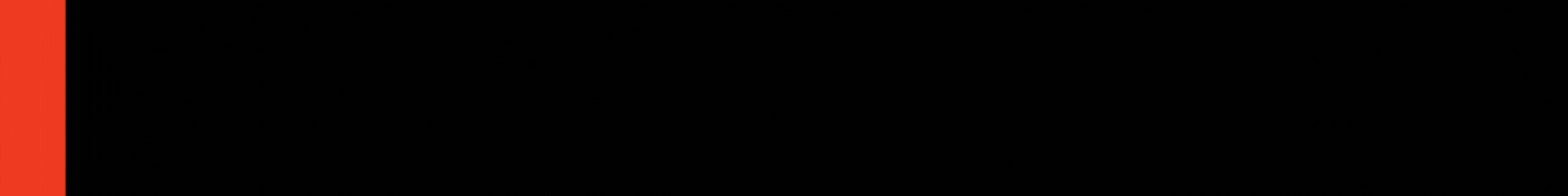অরক্ষিত উপকূলীয় অঞ্চলের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে
- প্রকাশিত: রবিবার, ২৩ নভেম্বর, ২০২৫
- ১১২ বার পড়া হয়েছে

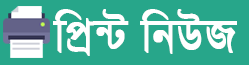
বিশেষ প্রতিনিধি : বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এক বিশাল উপকূলীয় অঞ্চল বিস্তৃত, যা দেশের অর্থনীতি, পরিবেশ ও জনজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উপকূলীয় অঞ্চলে দেশের ১৯টি জেলায় প্রায় ৩ কোটি মানুষের বসবাস। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৩২ শতাংশ উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। তবে উপকূলীয় অঞ্চল দেশের কৃষি, মৎস্য ও সামুদ্রিক অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হলেও জলবায়ু পরিবর্তন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়সহ বিবিধ দুর্যোগের কারণে উপকূলীয় জনপদ আজ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সূচক (২০১৯) অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭), আইলা (২০০৯), বুলবুল (২০১৯) এবং মোখা (২০২৩) উপকূলীয় জীবনের দুর্বলতা এবং অভিযোজন ব্যর্থতার দুর্বলতা প্রকাশ করেছে।
১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ৫ লক্ষাধিক প্রাণহানি, অসংখ্য পরিবার ধ্বংস ও উপকূলীয় জীবনব্যবস্থার বিপর্যয়ের স্মারক এই দিনটি আমাদের দুঃখময় স্মৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১২ নভেম্বর ‘উপকূল দিবস’ পালনের দাবি ও তাগিদটি তৈরি হয়েছে। সত্তরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে লাখো মানুষের প্রাণহানির বেদনা বহন করে চলেছে এই দিবস যা কেবল শোক পালনের জন্যই নয়, বরং এটি উপকূলের গুরুত্ব অনুধাবন করে এর শক্তিকে কাজে লাগানো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি দুর্যোগসহনশীল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের দিন। আমাদের উপকূলের শক্তিকে দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধির কেন্দ্রে আনতে হলে প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল কেবল দুর্যোগ এবং দুর্ভাগ্যের গল্প নয়, এটি শক্তি, সম্ভাবনা এবং সমৃদ্ধির আধার। প্রায় ১৯টি জেলার বিস্তৃত উপকূলজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা, কৃষি, মৎস্য এবং সামুদ্রিক অর্থনীতি জাতীয় প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।
উপকূলীয় অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সমুদ্র অর্থনীতি বা ‘সুনীল অর্থনীতি (ব্লু-ইকোনমি)’। বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক মৎস্য আহরণ, জাহাজ চলাচল, অফশোর সম্পদ ও পর্যটন শিল্প জাতীয় আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পাশাপাশি, চিংড়ি চাষ ও লবণ উৎপাদনের মতো কৃষিভিত্তিক খাতগুলো কোটি মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করছে। অন্যদিকে, সুন্দরবনসহ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বাংলাদেশের ‘প্রাকৃতিক ঢাল’ হিসেবে কাজ করে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় এই বন শুধু মানুষকেই নয়, গোটা উপকূলকে সুরক্ষা দেয়। এটি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধেও একটি প্রাকৃতিক প্রতিরোধক। সংগতকারণে এই অঞ্চল যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করছে, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায়ও অনন্য ভূমিকা রাখছে।
একটি টেকসই উপকূল গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন একটি সমন্বিত, মানবকেন্দ্রিক ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন কৌশল— যেমন: ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বাঁধ মজবুতকরণ, আধুনিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও টেকসই গৃহনির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন। টেকসই মৎস্য আহরণ পদ্ধতি, সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কঠোর নীতি অবলম্বন করা জরুরি।
উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ মূলত মৎস্য, কৃষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসাভিত্তিক জীবিকার ওপর নির্ভরশীল। ইউএনডিপি (২০২০)-এর তথ্যানুযায়ী উপকূলীয় জেলা বিশেষ করে খুলনা, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরার প্রায় ৩ কোটি মানুষ সরাসরি জলবায়ু ঝুঁকিতে রয়েছে। এই সকল উপকূলীয় অঞ্চলের ৭০% মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে কৃষি ও মৎস্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু বছরে গড়ে ৪-৫ বার তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকে। এখানকার বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক কাঠামো স্থানীয় ও জাতীয় উভয় পর্যায়ে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। তবে এই সম্ভাবনাময় অঞ্চল প্রতিনিয়ত একাধিক ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে। যেমন: ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙন এখানে জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল বাতাসের প্রকোপে এখানকার জনপদ তাদের প্রাণনাশের ঝুঁকিতে থেকে হারাচ্ছে আবাসস্থল ও পরিবহন যোগাযোগব্যবস্থা। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর তথ্য (২০২০) অনুযায়ী ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১,৩৮,০০০ জন নিহত হয়।
ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে প্রতি মৌসুমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে বনাঞ্চল, নষ্ট হচ্ছে বসবাসরত প্রাণীদের বাস্তুসংস্থান, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে প্রজননে। বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম, তলিয়ে যাচ্ছে আবাদি ফসল। কলেরা, ডায়রিয়া, টাইফয়েডের মতো পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে মহামারীতে রূপ নিচ্ছে। বাংলাদেশের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন (২০১৬) অনুযায়ী, দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় ৩০% এলাকা নিয়মিত জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও আন্তঃসরকার জলবায়ু পরিবর্তন প্যানেল (আিইপিসিসি, ২০১৬) এর তথ্যমতে, সাগরপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ১৭% উপকূলীয় এলাকা নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নদী ভাঙনের প্রভাবে গ্রামের পর গ্রাম বিলীন হয়ে যায় নদীগর্ভে, বাড়ে বাস্তুচ্যুত মানুষ যারা কর্মসংস্থানের জন্য ভিড় জমায় শহরে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (২০১৯)-এর তথ্য অনুসারে, প্রতিবছর গড়ে ৮,০০০-১০,০০০ হেক্টর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়। কর্মহীন মানুষের দরিদ্র্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, পুষ্টিহীনতা ও নিরাপত্তাহীনতার যার শিকার হয় নারী ও শিশুরা। উপকূলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও খরার প্রভাবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি ও মৎস্যখাত। ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে সুপেয় জলের সংকট। সাম্প্রতিক গবেষণা ও আন্তর্জাতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, নদীর লবণাক্ততা বাড়ার ফলে উপকূলীয় কৃষি, মৎস্যচাষ ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা তীব্র হচ্ছে এবং আগামী দশকে ঝুঁকি আরও বাড়বে। মাটি সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে (২০১৮) উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৮৩ লাখ হেক্টর জমির ৫৩% এখন লবণাক্ততায় আক্রান্ত এবং এর ফলে ধান, ডাল ও শাকসবজির উৎপাদন ২০-৩০% পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও উপকূলে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, বনায়ন হ্রাস ও মেগা প্রজেক্টের করনণ উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য ও বনজ সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে জীবিকার স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে। বিশ্বব্যাংক (২০২৪) অনুযায়ী, আগামী ২০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২৬ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে, যা বাংলাদেশের উপকূলীয় ১৮% ভূমি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি করছে।
উপকূল শুধু ভৌগোলিক অঞ্চল নয়, এটি এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যেখানে সুপ্ত রয়েছে সমুদ্রভিত্তিক সুনীল অর্থনীতির অপার সম্ভবনা। এই জীবনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও নীতিগত সমর্থন জরুরি। কেননা, উপকূল শুধু বাংলাদেশের সীমানা নয়, এটি আমাদের ভবিষ্যৎ টিকিয়ে রাখার মেরুদ-ও বটে। উপকূলের শক্তি কাজে লাগিয়ে দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ গড়া কেবলই একটি লক্ষ্য নয়, এটি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। উপকূলের সুরক্ষা মানেই নিরাপদ বাংলাদেশ। উপকূলকে কেন্দ্র করে প্রয়োজন নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, যেখানে উন্নয়ন হবে দুর্যোগসহনশীল, পরিবেশবান্ধব এবং মানবকেন্দ্রিক।