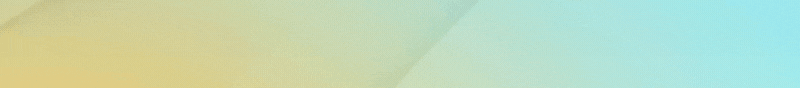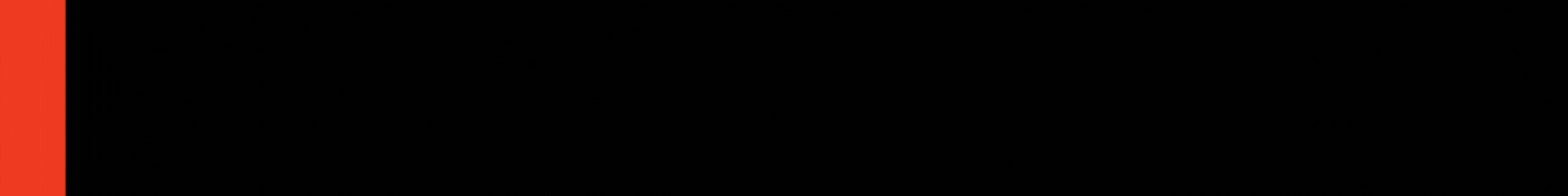পেটের দায় আর লোভে বিষাক্ত হচ্ছে সুন্দরবন
- প্রকাশিত: সোমবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২৫
- ১৪৫ বার পড়া হয়েছে

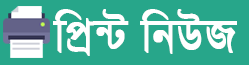
সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : “উপায় থাকলে কেউ সুন্দরবনে মাছ ধরতে যায় না। জেলেরা তো দাদনে জর্জরিত। জাল, নৌকা ওখান থেকে নেয়, এটা তো উসুল করতে হবে।”
সুন্দরবনের খালে অবৈধভাবে কীটনাশক ছিটিয়ে মাছ ধরার প্রবণতা বাড়ায় প্রতিনিয়ত হুমকির মুখে পড়ছে জীব-বৈচিত্র্য। অল্প সময়ে বেশি মাছ ধরা যায় বলে প্রান্তিক জেলেরা এ কাজে ঝুঁকছে। অভিযোগ আছে, বেশি লাভের লোভে কিছু আড়তদার জেলেদের দিয়ে এ কাজ করাচ্ছে।
বছরের একটি সময় বনে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার কারণে সুন্দরবন থেকে বনজীবী মানুষের আয়ের উৎস কমে গেছে। অথচ কোন সময়টায় নিষেধাজ্ঞা দিলে বনের লাভ হবে, সে সময়টায় বনের ওপর নির্ভরশীল মানুষ কী করবে- এসব নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত কোনো গবেষণা বা ডেটা নেই বলে বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য।
তারা বলছেন, গত এক দশকে সুন্দরবনের অর্থনীতির গতিপথ অনেকটাই বদলে গেছে। তাতে ভুক্তভোগী হচ্ছে বনজীবীরা। ফলে বনে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার সময় ‘বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারণ ও সমন্বয়’ করা জরুরি; পাশাপাশি বনের ওপর নির্ভরশীল মানুষদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন টেকনোলজি ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক মো. নাজমুল আহসান বলেন, “দুই দশক ধরে বলতে গেলে সুন্দরবনের রিসোর্স বলতে কিন্তু মাছ। এখানে বাঘ, হরিণ, গাছও বিক্রি হয় না। একসময় নিউজ প্রিন্ট, হার্ডবোর্ড মিলে গেওয়া গাছের চাহিদা ছিল। মানুষের জ্বালানি জন্য গরান, গোলাপাতার চাহিদা ছিল। এখন ইকনোমি চেইঞ্জ হয়ে গেছে। মার্কেট স্ট্রাকচার, মানুষের টেস্ট, প্রেফারেন্স বদলে গেছে।”
বনে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার কথা তুলে ধরে অধ্যাপক নাজমুল বলেন, “তখন বনজীবীদের হাতে সময় থাকে অল্প কিছু দিন। এ সময় দ্রুত ধরতে গিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের নিষিদ্ধ জাল, বিষ ব্যবহার করে (পানি নেমে যাওয়ার সময় খালের এক মাথায় বিষ দিয়ে অন্য মাথায় পেটুয়া জাল পাতা হয়)। বায়োলজিক্যালি পয়জন ফিশিংয়ে যে ক্ষতি হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।”
খুলনা অঞ্চলের বন সংরক্ষক ইমরান আহমেদ এই প্রতিবেদককে বলেন, প্রায়ই অভিযান চালিয়ে বিষ দিয়ে মাছ শিকারে জড়িত অসাধু মাছ ব্যবসায়ী ও জেলেদের গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু সেখানেও সমস্যা আছে।
“বিষ দিয়ে শিকার করা মাছ শনাক্ত করার মেশিন আমাদের কাছে নেই। এজন্য এ বিষয়ে প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করা যায় না। ফলে তারা দ্রুত আদালত থেকে জামিনে এসে আবার একই কাজ করেন।”
বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। ভারত ও বাংলাদেশ মিলিয়ে এই বন। বাংলাদেশ অংশের আয়তন ছয় হাজার ১৭ বর্গকিলোমিটার।
সুন্দরবনের ভেতরে ১৩টি বড় নদীসহ ৪৫০টির মত খাল রয়েছে। যা জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে এই বনে। এসব জলাধারে ভেটকি, রূপচাঁদা, দাঁতিনা, চিত্রা, পাঙ্গাশ, লইট্যা, ছুরি, মেদ, পাইস্যা, পোয়া, তপসে, লাক্ষা, কই, মাগুর, কাইন, ইলিশসহ ২১০ প্রজাতির সাদা মাছের দেখা মেলে।
এ ছাড়া এখানে গলদা, বাগদা, চাকা, চালী, চামীসহ ২৪ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। শিলা কাঁকড়াসহ ১৪ প্রজাতির কাঁকড়ার প্রজনন হয় এখানে। পাশাপাশি এখানে ৪৩ প্রজাতির মলাস্কা ও এক প্রজাতির লবস্টার রয়েছে।
সুন্দরবন পশ্চিম বনবিভাগের কর্মকর্তা এ জেড এম হাসানুর রহমান এই প্রতিবেদককে জানান, গোটা সুন্দরবনের ওপর প্রায় দেড় লাখ মানুষ কোনো না কোনোভাবে নির্ভরশীল। প্রতি বছর ১২ হাজারের বেশি জেলে পাস নিয়ে সুন্দরবনে মাছ ধরতে যায়।
এর সঙ্গে বাওয়ালি, মৌয়াল, ভোঁদর জেলে, রেণু শিকারি, ছন কাটার শ্রমিকদের যোগ করলে সংখ্যাটা কত হবে, সেই হিসাব তিনি তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেননি।
১৯৯৬ সালে বনের এক লাখ ৩৯ হাজার ৬৯৯ দশমিক ৪৯৬ হেক্টর ‘অভয়ারণ্য’ ঘোষণা করা হয়। ২০১৭ সালে ওই অভয়ারণ্যের আওতা বাড়ে। সুন্দরবনের অর্ধেকের বেশি এখন অভয়ারণ্য। পূবে কটকা, দক্ষিণে নীলকমল ও পশ্চিমে পুষ্পকাঠী। সব মিলিয়ে অভয়ারণ্য এলাকা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩ হাজার ২০০ বর্গকিলোমিটার।
বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এ বলা হয়েছে, ‘অভয়ারণ্য’ অর্থ কোনো এলাকা যেখানে বন্যপ্রাণী ধরা, মারা, গুলি ছোড়া বা ফাঁদ পাতা নিষিদ্ধ থাকবে এবং বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশবিস্তারের লক্ষ্যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন উদ্ভিদ, মাটি ও পানি সংরক্ষণের নিমিত্তে ব্যবস্থাপনা করা হবে।
এ আইনের চতুর্থ অধ্যায়ের ১৪(১) ধারায় উল্লেখ রয়েছে, কোনো ব্যক্তি অভয়ারণ্যে চাষাবাদ, শিল্পকারখানা স্থাপন, উদ্ভিদ আহরণ ও ধ্বংস করতে পারবেন না। বন্যপ্রাণীকে বিরক্ত বা ভয় দেখানো এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বিনষ্ট হতে পারে এরূপ রাসায়নিক ও গোলাবারুদ ব্যবহার করতে পারবেন না।
অভয়ারণ্যের বাইরে বনের অন্য অংশে প্রতিবছর ১ জুন থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত তিন মাস প্রবেশ ও মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা থাকে।
অভিযোগ রয়েছে, নিষেধাজ্ঞার সময়টাতে বনে অপরাধ বেড়ে যায় কয়েকগুণ। কারণ ওই সময় বনে দর্শনার্থী থাকে না; নির্ভয়ে মাছ ধরা যায়। এতে বনবিভাগের অসাধু কর্মকর্তারাও জড়িত থাকেন স্থানীয় এক শ্রেণির দালালের মাধ্যমে।
সুন্দরবনে নির্দিষ্ট সময়ে পাস নিয়ে জেলেদের মাছ ধরার অনুমতি রয়েছে। তবে তারা কী জাল ব্যবহার করবেন সেটা নির্ধারিত থাকে। পোনা বা রেণু আটকে যায় এমন জাল নিয়ে সুন্দরবনে প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
তারপরও মশারির মত প্রায় নিশ্ছিদ্র টানা বা বেহুন্দি জাল দিয়ে চিংড়ির পোনা ধরা হয়। এতে চিংড়ির সঙ্গে নানা জাতের মাছের পোনা ছাড়া সামুদ্রিক প্রাণীর লার্ভাও মারা পড়ছে। এই জাল ব্যবহার করার কারণ বেশি মাছ ধরা পড়ে।
তবে নিষেধাজ্ঞার সময়ে জেলেদের কীটনাশক দিয়ে খালে মাছ ধরার প্রবণতা বেশি। কারণ, এতে অল্প সময়ে বেশি মাছ আহরণ করা যায়। এক্ষেত্রে এক শ্রেণির অসাধু মাছ ব্যবসায়ীর বিনিয়োগ করার অভিযোগ আছে।
কয়েকজন জেলের সঙ্গে কথা হলে তারা জানান, ফসলের পোকা দমনের কীটনাশক ডায়মগ্রো, ফাইটার, রিপকর্ড ও পেসিকল বেশি ব্যবহার করা হয়; যা গোপনে জেলেরা নৌকায় করে নিয়ে যায়। ভাটার সময়ে যখন খাল শুকনো থাকে, তখন ভাত, চিড়া, রুটি, বিস্কুট কিংবা অন্য কোনো আধারের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে সেখানে ছিটিয়ে রাখা হয়। জোয়ারের পানির সঙ্গে মাছ আসে। সেই পানিতে কীটনাশক মিশে যায়। তখন খালের মাছ ভেসে উঠে।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন টেকনোলজি ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক নাজমুল আহসান বলেন, “বিষক্রিয়ায় মাছটা দুর্বল হয়ে পড়ে। মাছের ক্ষেত্রে পানি থেকে অক্সিজেন ফুলকার মাধ্যমে ডিফিউশন হয়ে ব্লাডে যায়। ডিজলভ অক্সিজেন থেকে ব্লাডে যায় ডিফিউজড অক্সিজেন। বিষের কারণে ফুলকাটা তখন ইন-অ্যাকটিভ হয়ে যায়; অন্য কোনো ক্ষতি হয় না, মাছটা অবশ হয়ে যায়। তবে বিষটা মাছের শরীরে থেকে যায়।”
নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সুন্দরবন সংলগ্ন কয়রা উপজেলার ৬ নম্বর কয়রা ইউনিয়নের বনজীবী আবু বক্কর বলেন, “বিষ দিয়ে মাছ শিকার করলে একসঙ্গে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। তবে বিষ দিয়ে মাছ ধরার পরে ওই খালে অনেক দিন কোনো মাছ ঢোকে না। কারণ খালে মাছের কোনো খাবার থাকে না। যে কারণে আমরা এখন মাছ কম পাচ্ছি।”
শ্যামনগর ধাতিনা খালি গ্রামের রমজান আলী ওকয়রা ইউনিয়নের বনজীবী আবু বক্কর বলেন, “বিষ দিয়ে মাছ শিকারের সঙ্গে বনবিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা জড়িত। বনের অভয়ারণ্যগুলোতেও জেলেদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ঘাট দেন তারা। দিন যত যাচ্ছে, তাদের ঘুষ তত বাড়ছে।
“টাকা না পেলে রাতভর ধরা মাছ ভোর হতেই বনের দালালদের মাধ্যমে ট্রলারে এসে নিয়ে যায় বনবিভাগের লোকজন। তাদের এসব অপকর্মের কথা বললে ধরে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়।”
সুন্দরবনের ঢাংমারী, মরাপশুর, জোংড়া, ঝাপসি, চড়াপুটিয়া, ভদ্দর, নিশানখালী, চ্যাওলাবগী, মাইঠা, বগা, কাগা, ভুমরখালী, কেওরাশুটি, ভদ্রা, নীলকমল, হরিণটানা, কোকিলমুনী, হারবাড়িয়াসহ চারটি রেঞ্জের আশপাশের বন সংলগ্ন এলাকার নদী ও সাতক্ষীরা রেঞ্জের কলাগাছিয়া, ডুবে কি, আন্দারমানিক ,খোবরাখালী ,ধানি বুনিয়া ,ফিরিঙ্গিয়া, চালিতাবাড়িয়া ,ঝিঙ্গাবাড়িয়া, দিংগি মারি , হাতী ভাঙ্গা, চুনকুড়ি ,দার গান, ১৮বে কি , কাছিঘাটা , ইলশেমারি, লটারি বেকি,হলদিবুনিয়া ,কালিরচর ,চোরার মেঘনা , পুষ্প কাটি, উলোবাড়িয়া ,তালপট্টি ,এই সমস্ত খালে কীটনাশক দিয়ে বেশি মাছ ধরা হয় বলে জেলেদের ভাষ্য। সাতক্ষীরা রেঞ্জের এই সমস্ত মাছ বিক্রি হচ্ছে শ্যামনগর উপজেলা কলবাড়ি ও সোনার মোড় মৎস আরোতে।
সুন্দরবন একাডেমির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির বলেন, “প্রভাবশালী সিন্ডিকেটের ছত্রচ্ছায়ায় এক শ্রেণির জেলে সুন্দরবনের ভেতরে ঢুকে বিষ দিয়ে মাছ শিকার করে। এতে শুধু মাছ নয়, পানি বিষাক্ত হয়ে অন্যান্য জলজ প্রাণীও মারা যাচ্ছে।”
অনেক ক্ষেত্রে জেলেরা মহাজনদের কাছ থেকে দাদন বা ঋণ নিয়ে বনে যান। ফলে তাদের বেশি মাছ ধরতে হয়। তাদের বাধ্য করা হয় কীটনাশক নিয়ে যেতে।
বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক জনপ্রতিনিধি মো. নূর আলম শেখ বলেন, আগে দেখা যেত অভয়ারণ্য এলাকায় একটি-দুটি দল বিষ দিয়ে মাছ ধরত। তারা মৎস্যজীবী ছিলেন।
“কিন্তু এখন সেখানে দাদনদাতা হয়ে গেছেন সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার স্থানীয় কিছু মৎস্য আড়তদার, মহাজন এবং কিছু রাজনৈতিক প্রভাবশালী নেতা। তারাই এখন বনবিভাগের সঙ্গে রফা করেন, বনের বিভিন্ন খাল জেলেদের কাছে ইজারা দেন।
“আর সাধারণ জেলেরা তাদের হয়ে মাছ ধরেন। ফলে কখনো আটক হলে, সাজা হলে হয় ওই জেলেদের। কিন্তু বনবিভাগ বা ওই প্রভাবশালীরা থেকে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু বনে এরা মূলত মৎস্য আড়তদার, মহাজনদের চাপে কৃষিকাজে পোকা দমনে ব্যবহৃত কীটনাশক নিয়ে যান”, যোগ করেন নূর আলম।
আড়তদারদের দাদন ব্যবসার সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি মোংলা বাজার মৎস্য সমিতির সভাপতি আফজাল ফরাজিও স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, “কিছু আড়তদার কয়েকটি চক্রকে নিয়মিত মোটা অঙ্কের দাদন দিয়ে সুন্দরবনে বিষ দিয়ে মাছ ধরতে পাঠায়।”
তবে আফজাল কারও নাম বলতে রাজি হননি।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন টেকনোলজি ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক নাজমুল আহসান বলেন, “উপায় থাকলে কেউ সুন্দরবনে মাছ ধরতে যায় না। জেলেরা তো দাদনে জর্জরিত। জাল, নৌকা ওখান থেকে নেয়, এটা তো উসুল করতে হবে।”
এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে হাজার পনের জেলে পরিবারকে চিহ্নিত করে নিষেধাজ্ঞার সময় সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় নিয়ে আসার ওপর জোর দেন তিনি।
সুন্দরবন সংলগ্ন শ্যামনগর চুনকুড়ি গ্রামের রেজাউল করিম মোংলা উপজেলার চিলা এলাকার জেলে গোলাম রসুল হাওলাদার সংসারের অসচ্ছলতার কারণে ছোটবেলা থেকেই সুন্দরবনের নদী-খালে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। তার প্রতিবেশীদের ৮০ শতাংশই সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বনে আর আগের মত মাছ বা অন্য আয়ের উৎস নেই বলে তার ভাষ্য। ফলে বনজীবীদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে।
রেজাউল করিম ও গোলাম রসুল বলেন, “এখন বনে শুধু মাছের ওপর নির্ভর করে আমাদের সংসার চলে না। বছরের একটা বড় সময় মাছ ধরা যায় না। পরিবার না খেয়ে থাকে। তখন তো কেউ সাহায্য করে না। আমরা আধপেটা থাকি।
“কেউ কেউ ঝুঁকি নিয়ে তখন হয়ত ধরতে যায়। প্রথম দিকে কেবল ছোট ছোট ভারানি খালগুলোতে কিছু জেলে বিষ দিয়ে মাছ ধরতেন। এখন দিন দিন তা বাড়ছে। ফলে এখন মাছ কম পাওয়া যাচ্ছে।
তিনি বলছিলেন, “বিষ দেওয়া মাছ ভাসার পর বড় মাছগুলো জেলেরা তুলে নেয়। কিন্তু ছোট মাছগুলো থেকে যায়। সেগুলো পাখি খাচ্ছে। তার ফলে প্রায়ই মৃত পাখি ভাসতে দেখা যায়।”
শ্যামনগর উপজেলার পার্সেমারি গ্রামের তাজুল ইসলাম ও মঠবাড়ি এলাকার বনজীবী আকবার সানা বলেন, এক শ্রেণির জেলে বিষ দিয়ে চিংড়ি ধরে গহীন সুন্দরবনে মাচা করে বনের গাছ পুড়িয়ে শুঁটকি তৈরি করে শহরে পাঠাচ্ছেন। সুন্দরী গাছের আগুন চিংড়ি শুকানোর জন্য বেশ ভালো। এতে শুকানো চিংড়ির রং অনেকটা লালচে হয়। বাজারে ওই চিংড়ির চাহিদা ও দাম বেশি।
হরিণ ধরার ক্ষেত্রেও অনেক সময় বিষ ব্যবহার করা হয় বলে কয়েকজন জেলে জানান।
ঘুষের বিনিময়ে বিষ দিয়ে মাছ শিকারে সহায়তা, জেলেদের হয়রানি করার অভিযোগে সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের কাশিয়াবাদ কর্মকর্তা সহ একাধিক চাঁদাবাজির মামলা করেছিলেন ভুক্তভোগীরা।
অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পরে তাকে পাটকোস্টা টহল ফাঁড়িতে বদলি করা হয়েছে বলে সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এ জেড এম হাসানুর রহমান।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক অধ্যাপক আবদুল্লাহ হারুন চৌধুরী বলেন, সুন্দরবনের যেসব খালে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়, তার বিষক্রিয়া সংশ্লিষ্ট এলাকায় চার মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত থাকে। এর ফলে জলজ প্রাণীদের প্রজনন ক্ষমতা কমে যাওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত ও সংখ্যা কমে যাচ্ছে।
“আবার এই কীটনাশক মিশ্রিত পানি ভাটার টানে যখন গভীর সমুদ্রের দিকে যায়, তখন সেই এলাকার মাছও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
অধ্যাপক আবদুল্লাহ বলেন, “কীটনাশক প্রয়োগের পর জেলেরা সেখান থেকে শুধু বড় মাছগুলো সংগ্রহ করেন। ছোট মাছগুলো তারা নেন না। কিন্তু এই ছোট মাছগুলো ছিল বড় মাছের খাবার। ফলে ওই এলাকার খাদ্যচক্রেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। মাছ ধরার এই প্রক্রিয়া আসলে বনের জলজ জীববৈচিত্র্যকেই বিপন্ন করে তুলেছে।”
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন টেকনোলজি ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক নাজমুল আহসান বলেন, দীর্ঘ মেয়াদে বিষ দিতে থাকলে পরিবেশে এটা থেকে যায়। যদি পরিবেশে প্রাণীগুলো না থাকত, তাহলে হয়ত ‘ওয়াশ আউট’ হয়ে যেত। কিন্তু এটা খাদ্যচক্রে থেকে যাচ্ছে।
“সরাসরি একটা বিশেষ মাছের শরীরে যাচ্ছে, সেই মাছ আপনি ধরছেন। আরেকটা হচ্ছে, ফুড চেইনে মাটির তলদেশে ছোট ছোট প্রাণী থাকে তাদের ক্ষেত্রেও। স্লো হলেও এর ইমপ্যাক্ট কী হবে তা গবেষণার বিষয়। খারাপ যে হবে তাতে সন্দেহ নেই; তবে কোন স্কেলে, কতটুকু হবে তা গবেষণার বিষয়।”
এই বিপদগুলোর বিষয়ে জেলেদের বোঝানোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নাজনীন নাহার বলেন, “শুধু মাছ নয়, অনেক জলজ প্রাণী রয়েছে- বিষ ব্যবহার করলে তা ক্ষতি হবে- তা বুঝাতে হবে। সচেতনতার বিকল্প নেই এখানে।”
বিষাক্ত পানির মাছ খেলে মানুষের পেটের পীড়াসহ কিডনি ও লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং তা ক্যান্সারেরও ঝুঁকি তৈরি করে। সাম্প্রতিক সময়ে খুলনা অঞ্চলে এ ধরনের রোগী বেড়েছে বলে জানালেন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) নিয়াজ মুস্তাফি চৌধুরী।
তিনি বলেন, “তবে সুন্দরবনের নদী ও খালে বিষ প্রয়োগের মাছ খেয়েই এমনটা হচ্ছে, তা বলার মত তথ্য-উপাত্ত হতে নেই, কারণ এ বিষয়ে কোনো গবেষণা হয়নি।”
তৎকালীন শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক শেখ আবু শাহীনও বললেন, “আমাদের কাছে এ ব্যাপারে পরিসংখ্যান নেই। তবে কিডনি, লিভার, ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী আগের চেয়ে বেড়েছে।”
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন টেকনোলজি ডিসিপ্লিনের নাজমুল আহসান সুন্দরবনের নিষেধাজ্ঞার সময় ও বিকল্প কর্মসংস্থান নিয়ে ভাবার তাগিদ দিয়েছেন।
তার অভিমত, “আসলে ব্যান পিরিয়ডটা (নিষেধাজ্ঞার সময়) সায়েন্টিফিক নয়। এক মাস, দুই মাস, তিন মাস বন্ধ- ঠিক আছে। কম সময়ও হতে পারে আবার বেশি সময়ও হতে পারে। কিন্তু আমার জানা মতে এ নিয়ে কোনো গবেষণা নেই, ডেটা নেই। খালগুলোতেও বন্ধ থাকে, ধারণা করা হয় হয়ত সে সময়টা ব্রিডিং টাইম। কিন্তু কোনো ডেটা নেই। এটা সায়েন্টিফিক হতে হবে।
“একদিকে পোনা সংগ্রহ, আরেকদিকে বড় মাছ শিকার- এভাবেও চললে সুন্দরবনের রিসোর্স সাসটেইন করবে না। তখন বনবিভাগ তিন মাসের মত করে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, মৎস্য বিভাগের নিষেধাজ্ঞা থাকে সমুদ্রে, ৬৫ দিনের মত। নানা ধরনের এনফোর্সমেন্ট ও লিগ্যাল ইন্সট্রুমেন্ট রয়েছে। তখন তাদের লাইভলিহুড সীমিত হয়ে আছে। তখন কিছু সুযোগ সন্ধানী (ডিপো, আড়তদার, মহাজনের প্রলোভনে অনেক জেলে) স্বল্প সময়ে দ্রুত মাছ ধরার চেষ্টা করে।
তিনি বলেন, নিষেধাজ্ঞার সময়ে বনজীবীদের বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বন ও মৎস্য খাতের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।
তবে ‘নিষেধাজ্ঞা বৈজ্ঞানিকভাবে দেওয়া হয় না’- এই অভিমতের সঙ্গে একমত নন আঞ্চলিক বন কর্মকর্তা মিহির কুমার দো।
তিনি বলেন, “আমরা জুন থেকে অগাস্ট- এই তিন মাস নিষেধাজ্ঞার আওতায় রাখি সুন্দরবনকে। এই সময়ে নদী ও সমুদ্রেও ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা থাকে। এটা মৎস্য বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মতামত নিয়েই করা হয়। কারণ, এই সময়টা মাছের প্রজননের সময়।
“শুধু মাছ নয়, বর্ষাকাল উদ্ভিদ জগতের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে বনের সব প্রাণ যেন নিজের মত করে বিস্তার করতে পারে সেটাও আমাদের নজরে থাকে। নিষেধাজ্ঞার সময়টা সবার সঙ্গে সমন্বয় করেই দেওয়া হয়।
তবে নিষেধাজ্ঞার সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যাপারে একমত পোষণ করে ইমরান আহমেদ এই প্রতিবেদককে বলেন, “দেখুন, যারা বনজীবী তাদের তো পেট আছে, পরিবার আছে। বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি আছে। টানা ৯০ দিন তারা মাছ ধরতে পারেন না, বনে যেতে পারেন না। তখন খাবে কী? পেট তো সবার আছে। ফলে আমি তাদের বিকল্প ব্যবস্থার পক্ষে। “
নদী এবং সমুদ্রে যখন নিষেধাজ্ঞা চলে তখন মৎস্য অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলেদের সেই সময়ের জন্য চাল কিংবা অন্য সহায়তা দিয়ে থাকে। কিন্তু সুন্দরবনের জেলেদের জন্য সেই ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই।
মিহির কুমার দো বলেন, “আমরা বনবিভাগের পক্ষ থেকে প্রায় এক বছর আগে মৎস্যসম্পদ অধিদপ্তরে এ ব্যাপারে সুপারিশ করে পাঠিয়েছি। আমরা বনের ওপর নির্ভরশীল জেলেদের ৯০ দিনের জন্য সহায়তা দেওয়ার কথা বলেছি। কিন্তু সেটি এখনও গৃহীত হয়নি। হলে ভালো হবে। জেলেরা আপৎকালীন সময়ে কিছুটা স্বস্তি পাবেন।”
বিকল্প ব্যবস্থা না থাকার কারণে জেলেদের নিষিদ্ধ সময়ে কীটনাশক দিয়ে মাছ ধরার প্রবণতা বাড়ছে কিনা; কিংবা এর কোনো প্রভাব জেলেদের জীবনে পড়ে কিনা- এ প্রশ্নে তিনি বলেন, “আমি মনে করি, পড়ে। অনেকে বন কর্মীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পেটের দায়ে, সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে ঝুঁকি নিয়ে বনে ঢোকে। কেউ যাতে না দেখে এ কারণে খুব অল্প সময়ে তাকে মাছ ধরতে হয়। এ কারণে জেলেরা হয়ত কীটনাশক ব্যবহার করে।
“এ ছাড়া একজন নিবন্ধিত জেলে একবার পাস নিয়ে বনে প্রবেশ করলে এক সপ্তাহ মাছ ধরতে পারেন। সময়টা খুব বেশি না। এ কারণেও হয়ত তারা বেশি মাছ ধরতে চান। এই লোভ থেকেও তারা কীটনাশক ব্যবহার করতে পারে”, যোগ করেন মিহির কুমার দো।
খুলনা অঞ্চলের বন সংরক্ষক ইমরান আহমেদ বলেন, বিষ দিয়ে মাছ শিকারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রতিটি স্টেশন ও ফাঁড়ির বনরক্ষীদের কঠোর নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে।
“অনেকগুলো সংস্থা এখানে অভিযান চালায়। সুন্দরবনের বিভিন্ন বিভাগ অভিযান চালায়। মামলা হয়। তবে মামলার সংখ্যা এই মুহূর্তে বলা কঠিন।”
বিষ দিয়ে মাছ শিকারের সঙ্গে বনবিভাগের কর্মকর্তা ও সদস্যদের জড়িত থাকার অভিযোগের বিষয়ে প্রশ্ন করলে মিহির কুমার বলেন, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেন তারা।
আর খুলনা জেলা এই প্রতিবেদককে বলেন, সুন্দরবনে সরাসরি অভিযানের অনুমতি না থাকায় মৎস্য বিভাগ সেখানে অভিযানে যেতে পারে না।
খুলনার পুলিশ সুপার এই প্রতিবেদককে বলেন, মাঝেমধ্যে এসব ঘটনায় অনেককে কীটনাশক, কীটনাশক মিশ্রিত মাছসহ আটক করা হয়। আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
তবে অপ্রতুল লোকবল দিয়ে সুন্দরবনের সব নদী-খাল পাহারা দেওয়া সম্ভব নয় মন্তব্য করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এই প্রতিবেদককেবলেন, প্রশাসন যতটুকু সম্ভব আইন প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে।
“বনবিভাগসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছি আমরা। ব্যক্তিগতভাবে আমি সভা-সমাবেশে কীটনাশক প্রয়োগের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে স্থানীয় মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি।” তারপরও বলছি সুন্দরবন রক্ষার দায়িত্ব এদেশের ১৮ কোটি মানুষের সুন্দরবন আমাদের জাতীয় সম্পাদ জাতীয় সম্পত্তিকে রাখার দায়িত্ব আপনার আমার সকলের সুন্দরবন যদি না থাকে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে একাংশের মানুষ বসবাস করতে পারবে না সে কারণে সুন্দরবনকে টিকিয়ে রাখতে দলমত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।