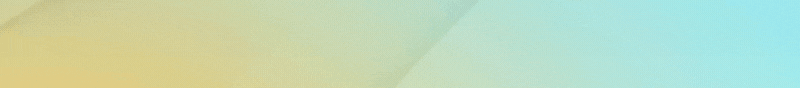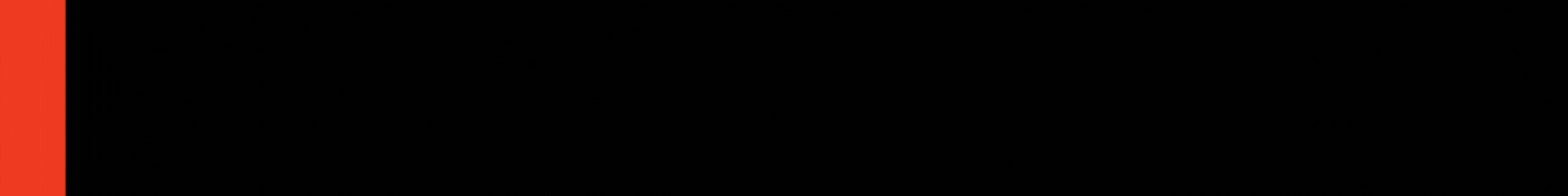জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার শঙ্কা সুজন-সখীদের
- প্রকাশিত: মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৫
- ৫৮ বার পড়া হয়েছে

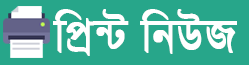
বিশেষ প্রতিনিধি : সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণের গ্রাম বুড়িগোয়ালিনী। দেশের দক্ষিণে সর্বশেষ জনপথ নীলডুমুর বাজার থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় ৬০০ গজ এগোলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়িবাঁধের ভেতরে দেখা মেলে সত্তরোর্ধ্ব জাহানারা বেগমের টিনের ঘর। এক কক্ষে থাকেন জাহানারা ও তাঁর স্বামী মোসলেম গাজী; অন্যটিতে থাকেন তাদের মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ে এবং দুই নাতি-নাতনি সুজন ও সখী। বাড়িটি সুজন-সখীদের ঘর বলেও পরিচিত।
বুড়িগোয়ালিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে সুজন ও সখী। বয়সে দুই বছরের ব্যবধান থাকলেও একসঙ্গে স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন তাদের নানি। কথা হয় সুজন ও সখীর সঙ্গে। তারা জানায় তাদের বেঁচে থাকার দুঃসহ লড়াইয়ের কথা। স্কুলে না গিয়ে কখনও কখনও নদীতে নৌকায় কাটে তাদের সময়। নানির সঙ্গে মাছ বিক্রির পাশাপাশি কখনও বা নীলডুমুর বাজার ও আশপাশে বাড়িগুলোয় ভিক্ষা করে তারা। কখনও বা মজুরিভিত্তিক (অনিয়মিত) কাজ করে।
জাহানারা বেগম এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘সুজন ও সখীর মা পাগল। ওদের বাবা আরেক জায়গায় বিয়ে করেছে। দুই নাতি-নাতনিকে শিক্ষিত করতে চাইলেও তারা পড়তে চায় না। অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে।’
এই দুই শিশু জানায়, মাঝেমধ্যে পেটের পীড়া ও জ্বর-সর্দি-শ্বাসকষ্ট লেগে থাকে তাদের। এ ছাড়া চুলকানি ও ঘা-পাঁচড়া নিত্যসঙ্গী। পড়াশোনায়ও মনোযোগ থাকে না তাদের।
সুন্দরবনসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকাগুলো ঘুরে দেখা যায়, রোগব্যাধির সঙ্গে লড়াই শুধু সুজন-সখীর নয়; হাজারো শিশুর পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যরাও নানা ধরনের শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। সাতক্ষীরার উপকূলীয় তিন উপজেলা শ্যামনগর, আশাশুনি ও কালিগঞ্জ এবং খুলনার উপকূলীয় দুই উপজেলা কয়রা ও দাকোপে চলতি বছর ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত ৭৭ হাজার ৩০৪ শিশু সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসা নিয়েছে। এর বাইরেও অনেক শিশু-কিশোর বেসরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়েছে। অনেক শিশু ও কিশোর-কিশোরী রয়েছে, যারা কোনো ধরনের চিকিৎসাসেবাই গ্রহণ করছে না। এদিকে খুলনা ও সাতক্ষীরায় ৪৭৮ চিকিৎসকের পদ থাকলেও কর্মরত মাত্র ১৭০ জন। এর মধ্যে পাঁচ উপজেলায় শিশু বিশেষজ্ঞ আছেন মাত্র একজন। অনেক উপজেলায় সরকারি ওষুধের সরবরাহ নেই।
শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত সুজন-সখীসহ ২৬ হাজার ১৭৯ শিশু জলবায়ুর প্রভাবজনিত নানা রোগে চিকিৎসা নিয়েছে। এর মধ্যে চর্মরোগে ৯ হাজার ৪৮৫ শিশু, জ্বর ৮ হাজার ২৬৯, সাধারণ সর্দি-কাশি ৭ হাজার ৭১৫, ডায়রিয়াজনিত রোগে ৪ হাজার ৯৭৯, অপুষ্টিজনিত ১ হাজার ৭৯৫, কান পচা ৮৭৫, নিউমোনিয়ায় ৪৩৩ শিশুকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। উপকূলীয় এলাকায় শিশুদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা শুধু শ্যামনগরেই নয়, দেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলার ৮৭টি উপজেলায় এ সমস্যা প্রকট।
জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিশুর জন্য জলবায়ু ঝুঁকি সূচক বা চিলড্রেনস ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৩ দেশের মধ্যে ১৫তম। শিশুর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু’ভাবেই প্রভাব পড়ছে। সারাবিশ্বে পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের মোট রোগের ৮৮ শতাংশ হয় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে।
জার্মান ওয়াচ গ্লোবালের জলবায়ু ঝুঁকি সূচক (সিআরআই-২০১৭) অনুযায়ী বাংলাদেশ শীর্ষ ১০টি দেশের একটি।
পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, উপকূলের ১৯টি জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বেশি। এ তালিকায় আছে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, গোপালগঞ্জ, যশোর, ঝালকাঠি, লক্ষ্মীপুর, নড়াইল, নোয়াখালী, পিরোজপুর, শরীয়তপুর ও পটুয়াখালী। জেলাগুলোর ৭১০ কিলোমিটারজুড়ে উপকূলীয় এলাকা। মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ বাস করে এসব অঞ্চলে। তারা মৎস্য, কৃষিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছেন। নদী ও সুন্দরবনের নোনাপানির সঙ্গেই জীবনযাপন করতে হয় তাদের। ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়িয়ে তুলেছে এসব এলাকার ফসলহানি, মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি, বাস্তুচ্যুতিসহ বিভিন্ন সমস্যা। এসবের বিরূপ প্রভাব পড়ছে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর শিশুর ওপর।
সুন্দরবনসংলগ্ন খুলনার দাকোপ উপজেলার শিবসা ও সুতারখালী নদীর মোহনায় কালাবগি গ্রাম। সরেজমিন দেখা যায়, কমবয়সী শিশুর প্রায় সবার শরীর জীর্ণ। মাথার চুল আঠালো, চোখ ফ্যাকাসে, ত্বক রুক্ষ ও শুষ্ক। কলেজ শিক্ষার্থী কয়রার জীবন মণ্ডল জানান, অধিকাংশ শিশু মা-বাবার সঙ্গে নদীতে মাছ ধরে। শিশুরা বিশেষ করে নদী থেকে বাগদা ও গলদা চিংড়ির রেণু আহরণ করার জন্য জাল টেনে থাকে। প্রায় প্রতিদিনই চার থেকে ছয় ঘণ্টা তারা পানিতে থাকে। এ জন্য প্রায় শিশুর চেহারা কালচে ধরনের হয়। তাদের চামড়ায় নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। ত্বক শুষ্ক হওয়ার পাশাপাশি চুলকানি, ঘা-পাঁচড়া লেগেই থাকে। তাদের মাথার চুলও অনেকটা আঠালো হয়ে যায়।
২০১৯ সালে দেশের ১৪টি জেলার ৪২টি উপজেলাকে হার্ড টু রিচ (এইচটিআর) বা দুর্গম এলাকা ঘোষণা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। খুলনার দাকোপ ও কয়রা এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর, আশাশুনি ও কালিগঞ্জ আছে এগুলোর মধ্যে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং অবকাঠামো সংকটে এই পাঁচ উপজেলায় স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিকূল আবহাওয়ায় উপজেলাগুলোর প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছানো কঠিন। পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই। কাগজে-কলমে চিকিৎসক থাকলেও অনেকে নিয়মিত কর্মস্থলে থাকেন না। স্থানীয় বাসিন্দাদের হেঁটে, অস্থায়ী বাঁশের সেতু পেরিয়ে বিশাল পথ অতিক্রম করতে হয়। অথবা নৌকা নিয়ে নিকটতম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হয়।
চলতি বছরের ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত খুলনার কয়রায় ১৫ হাজার ৩৪৮, দাকোপে ১৬ হাজার ৫৪৪ এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগরে ২৬ হাজার ১৭৯, আশাশুনি ১১ হাজার ৪২৫ ও কালিগঞ্জে ৭ হাজার ৮০৮ শিশুকে চিকিৎসা দেওয়া হয়; যা গত বছরের চেয়ে প্রায় ১১ হাজার বেশি।
সুন্দরবনসংলগ্ন উপকূলীয় পাঁচটি উপজেলায় চিকিৎসক সংকট প্রকট। দাকোপে ৩১ চিকিৎসকের বিপরীতে ৯ জন, কালিগঞ্জে ৩৩ জনের মধ্যে ৮, শ্যামনগরে ৩৩ জনের মধ্যে ১২, কয়রায় ২৯ জনের মধ্যে ১০ এবং আশাশুনিতে ২১ জনের মধ্যে ৫ জন কর্মরত। এসব উপজেলার মধ্যে শুধু কয়রা উপজেলায় একজন শিশু বিশেষজ্ঞ কর্মরত। কয়েকটি উপজেলায় সরকারিভাবে ওষুধের সরবরাহ নেই।
এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে দাকোপ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডা. সুদীপ বালা এই প্রতিবেদককে বলেন, উপকূলের মানুষের রোগের ধরন ও অন্য এলাকার রোগের ধরন আলাদা। উপকূলের শিশুরা বেশি আক্রান্ত হয়। এখানে বিশেষ করে ডায়রিয়া, আমাশয়, পেটের পীড়া, চোখের উপরিভাগের রোগ, আলসার, চর্মরোগ, দাঁত, চুল, নখের রোগ বেশি। গুরুতর রোগীদের খুলনা সদর হাসপাতালে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।
কালিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এখানে পক্ষ থাকে এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘সরকারিভাবে ওষুধ সরবরাহ নেই। এক সপ্তাহ ধরে কোনো ওষুধ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এতে চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে।’
এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মো. আবু জাফর এই প্রতিবেদককে।বলেন, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতায় অনেক কিছু ইচ্ছা থাকলেও করা যাচ্ছে না। তবে মন্ত্রণালয় নতুন চিকিৎসক নিয়োগের বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে। শূন্য পদের সংখ্যা ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। তিনি জানান, উপকূলীয় এলাকার শিশুদের জন্য এ মুহূর্তে সরকারের কোনো বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন নেই।
খুলনা, সাতক্ষীরা, ভোলাসহ উপকূলীয় জেলাগুলোতে জলবায়ুর পরিবর্তন ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। ঘন ঘন দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে মানুষ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সংকট আরও ঘনীভূত করছে। খুলনার কয়রা নদী-তীরবর্তী হড্ডার শিল্পী মণ্ডল জানান, তাঁর সর্দি, কাশি সারাবছর লেগে থাকে। এমনকি তাঁর দুই বছর বয়সী মেয়েটিরও হাত ফেটে সব সময় রক্ত ঝরে।
সেভ দ্য চিলড্রেনের এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ডায়রিয়া, অপুষ্টি ও ম্যালেরিয়ায় অধিক হারে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। উপকূলের কোমলমতি শিশুরা ভুগছে বেশি। আর্থসামাজিক অবস্থা ও সমস্যার সঙ্গেও শিশুরা খাপ খাওয়াতে গিয়ে অসহায় হয়ে পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে দেশের প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ শিশুর জীবন ও ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে। এর মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী ৪৫ লাখ শিশুর জীবনে ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। এদিকে উপকূলীয় অঞ্চলসহ সারাদেশে সাড়ে তিন কোটির বেশি শিশুর রক্তে বিপজ্জনক মাত্রায় সিসার অস্তিত্ব পাওয়ার কথা জানিয়েছে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর), আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) এবং ইউনিসেফ। ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ। গত ৫ নভেম্বর এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
জলবায়ু বিশেষজ্ঞ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ এই প্রতিবেদককে।বলেন, বৈশ্বিকভাবে বাংলাদেশ বিশ্বে জলবায়ু সংকটের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। সমুদ্র-তীরবর্তী এলাকাগুলো নোনাপানির কারণে জীববৈচিত্র্য হারাচ্ছে। জনজীবনেও মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। আমাদের শিশুরা এই ক্ষতির বাইরে নয়। এর জন্য মোটাদাগে উন্নত বিশ্ব দায়ী। তবে আমাদের সরকারেরও দায় আছে। উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে, যেগুলো পরিবেশ বিপর্যয় ত্বরান্বিত করতে শুরু করেছে। তিনি আরও বলেন, সরকার শিশুসহ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর যথাযথ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে পারছে না। সার্বিকভাবে চিকিৎসাসেবা অপ্রতুল এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এ জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবিলায় সরকারকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করতে হবে।
এ প্রসঙ্গে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শিশুসহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা সব সময় হুমকির মুখে থাকে। তাই একটি কার্যকর পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। অন্তর্বর্তী সরকার এ লক্ষ্যে কাজ করছে।