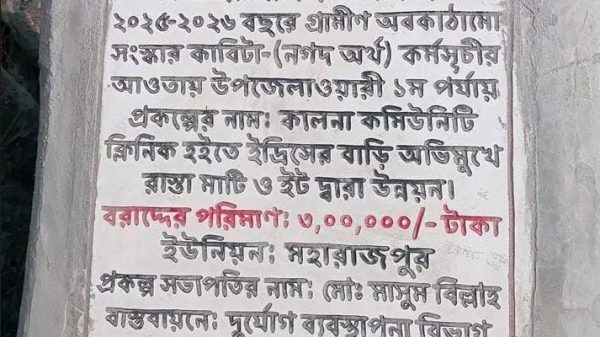উপকূলের খাদ্যসংকট নিয়ে ভাবছেন কি নীতিনির্ধারকেরা?
- প্রকাশিত: রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
- ১০১ বার পড়া হয়েছে


সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : যখন ক্ষুধা ও অপুষ্টিমুক্ত বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হবে, তখন বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদনের সাফল্যগাথা নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রশংসিত হবে। ধান উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়, মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার মতো অর্জনগুলো আমাদের জাতীয় গর্বের ভিত্তি। কিন্তু এই উজ্জ্বল পরিসংখ্যান আর উদযাপনের আড়ালেই লুকিয়ে আছে এক গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন বাস্তবতা। দেশের দক্ষিণ উপকূলের কয়েক কোটি মানুষের জীবন আজ লবণাক্ত পানির আগ্রাসনে বিপন্ন। তাই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, আমাদের নীতিনির্ধারকেরা কি উপকূলের এই নীরব খাদ্যসংকট নিয়ে গুরুত্বের সাথে ভাবার ফুরসত পাচ্ছেন?
জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার সার্বিক চিত্রটি একটি বড় ক্যানভাসের মতো, যেখানে মোটা দাগের অর্জনগুলো সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলে উপকূলীয় অঞ্চলের ছবিটিতে অসংখ্য ক্ষতচিহ্নে ভরা। এটি এমন এক প্যারাডক্স, যা আমাদের উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে একটি বড় প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেয়। যে অঞ্চল দেশের মোট আবাদী জমির এক-চতুর্থাংশেরও বেশি ধারণ করে দেশের খাদ্যভা-ারকে সমৃদ্ধ করছে, সেই অঞ্চলের মানুষই আজ ক্রমবর্ধমান খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতার শিকার।
বাংলাদেশের উপকূলীয় ১৯টি জেলা একসময় পরিচিত ছিল প্রাচুর্যময় ভূমি হিসেবে। এখানকার উর্বর পলিমাটি আর জালের মতো ছড়িয়ে থাকা নদী-নালার আশীর্বাদ যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি মানুষের জীবিকার জোগান দিয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে, এই অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা ছিল প্রকৃতি-নির্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্ষার মিঠা পানিতে আমন ধানের সবুজ গালিচা বিছিয়ে যেত দিগন্তজুড়ে, যা ছিল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রধান খাদ্যশস্য এবং আয়ের উৎস। শুষ্ক মৌসুমে কিছু জমি পতিত থাকলেও, খালের পাড়ে বা নিচু জমিতে ফলত ডাল, তেলবীজসহ নানা ধরনের রবিশস্য।
তবে এই মাঠের ফসলের পাশাপাশি উপকূলীয় খাদ্য নিরাপত্তার এক নীরব অথচ শক্তিশালী স্তম্ভ ছিল প্রতিটি বাড়ির আঙিনায় গড়ে ওঠা বসতভিটার কৃষি। যখন প্রাকৃতিক কারণে বা অন্য কোনো বিপর্যয়ে মাঠের ফসলহানি হতো, তখন এই বসতভিটাই হয়ে উঠত পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানোয় প্রধান সহায়ক। এখানে সারি সারি নারিকেল, পেয়ারা, আমড়া, সফেদা আর কুলের গাছ ছায়া দিত; মাচায় ঝুলত লাউ, কুমড়ো, শিম; আর উঠোনে চরে বেড়াত হাঁস-মুরগির দল। পুকুরে ভরা ছিল রুই, কাতলা, শিং, মাগুরের মতো মিঠা পানির মাছ। বিশেষ করে নারীরা এসবের মাধ্যমে পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করতেন। একটি পরিবার তাদের প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, সবজি থেকে শুরু করে মাছ-মাংস-ডিম-দুধ পর্যন্ত নিজেরাই উৎপাদন করত, যা এক স্থিতিশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি টিকিয়ে রেখেছিল।
আশির দশক থেকে বাংলাদেশের উপকূলে শুরু হওয়া তথাকথিত ‘নীল বিপ্লব’ ছিল এক পরিবেশগত বিপর্যয়ের সূচনা। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা ও মুনাফার প্রলোভনে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটের হাজার হাজার হেক্টর উর্বর ধানক্ষেত লবণাক্ত পানির ঘেরে পরিণত হয়। চিংড়ি দ্রুত অন্যতম প্রধান রপ্তানি খাতে পরিণত হলেও, এর পেছনে জমি, পানি ও মানুষের দুর্ভোগের ইতিহাস দীর্ঘ। চিংড়ি চাষে নদীর লবণাক্ত পানি প্রবেশ করানোর ফলে আশপাশের কৃষিজমি ও ভূগর্ভস্থ পানি দূষিত হয়। ফলে ধান, শাকসবজি ও গবাদিপশু পালন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কৃষকেরা জীবিকা হারিয়ে শহরের বস্তিতে পাড়ি দেন, আর তাদের ফেলে যাওয়া অনুর্বর জমি আরও চিংড়ি ঘেরে পরিণত হয়।
উপকূলে আজ সবচেয়ে বড় সংকট লবণাক্ততা। এটি কৃষি উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে, মিঠাপানির অভাব তৈরি করেছে এবং মানুষের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, ডাইরিয়া ও গর্ভকালীন জটিলতার মতো স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়িয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লবণাক্ততা আরও বিস্তৃত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন, ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে দেশের প্রায় ১১ শতাংশ ভূমি ডুবে যাবে এবং কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। জলবায়ু–জনিত অভিবাসন ক্রমেই তীব্র আকার নিচ্ছে। গ্রাম থেকে শহরে এক সংকট থেকে অন্য সংকটে মানুষ ঢুকে পড়ছে।
পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক এই সংকটের সবচেয়ে করুণ শিকার হচ্ছে উপকূলের শিশুরা। খুলনা ও বাগেরহাটের মতো জেলাগুলোতে শিশু অপুষ্টির চিত্র যেকোনো বিবেকবান মানুষকে নাড়া দেবে। বাংলাদেশে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে অপুষ্টি একটি গুরুতর ও দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা। তবে জাতীয় পর্যায়ের তুলনায় উপকূলীয় অঞ্চলে শিশুদের দীর্ঘমেয়াদী অপুষ্টির চিত্রটি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। যেখানে জাতীয়ভাবে শিশুদের মধ্যে খর্বাকৃতির (স্টান্টিং) হার প্রায় ২৪%, সেখানে উপকূলীয় অঞ্চলে এটি ৩১% পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই উচ্চ হার নির্দেশ করে যে শিশুদের দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলের সমস্যার মূল কারণ হলো লবণাক্ত মাটি, বন্যা ও সাইক্লোনের নিয়মিত আঘাত, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশনের সীমাবদ্ধতা, দারিদ্র্য এবং খাদ্যের বৈচিত্র্যের অভাব। এর ফলে স্থানীয় জনগণ দীর্ঘমেয়াদী খাদ্যসংকট ও পুষ্টি অভাবের শিকার হচ্ছে, যা শিক্ষার সুযোগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য পরিস্থিতিকেও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে।
এই বিপর্যয়ের মূল কারণ খাদ্যাভ্যাসের কাঠামোগত অবনতি। লবণাক্ততার কারণে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পুষ্টিকর খাবার যেমন তাজা শাকসবজি, মৌসুমি ফল, দেশি মুরগির ডিম এবং মিঠা পানির মাছের উৎপাদন ও ভোগ দুটোই অনেক কমে গেছে। যে পরিবারগুলো একসময় খাদ্য উৎপাদক ছিল তারাই এখন খাদ্য মূল্যস্ফীতির শিকার হয়ে নিজেদের সন্তানদের মুখে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার তুলে দিতে পারছে না। পরিবেশগত বিপর্যয় জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে, জীবিকার অভাব ক্রয়ক্ষমতা কমাচ্ছে, এবং ক্রয়ক্ষমতার অভাবে শিশুরা অপুষ্টির শিকার হচ্ছে, যা তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিচ্ছে।
এই গভীর সংকট থেকে উত্তরণের জন্য একটি সমন্বিত ও বহুমুখী কৌশল অপরিহার্য। আশার কথা হলো, নীতিগত পর্যায়ে এর স্বীকৃতি রয়েছে। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এবং জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার মতো শক্তিশালী নীতি কাঠামো আমাদের আছে, যেখানে উপকূলের চ্যালেঞ্জগুলোকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতেও অগ্রগতির কোনো কমতি নেই। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইজজও) লবণ-সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনে বিপ্লব এনেছে। বিআরআরআই ধান-৬৭, এবং সম্প্রতি উদ্ভাবিত বিআরআরআই ধান-৯৭ ও বিআরআরআই ধান-৯৯-এর মতো জাতগুলো উচ্চ লবণাক্ততা সহ্য করে হেক্টর প্রতি ফলন ১ থেকে ২ টন পর্যন্ত বাড়াতে সক্ষম। এর পাশাপাশি, পানিবদ্ধ জমিতে উঁচু বেড তৈরি করে সবজি এবং পাশের নালায় মাছ চাষ করার ‘সরজন পদ্ধতি’, বৃষ্টির পানি পুকুর ও খালে সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহার করার মতো দেশীয় ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তিগুলো কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।
কিন্তু মূল প্রশ্নটি হলো এই নীতি, পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তিগুলো কি তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে? লবণ-সহনশীল ধানের বীজ কি প্রান্তিক কৃষক সময়মতো এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পাচ্ছেন? অপরিকল্পিত চিংড়ি ঘেরের আগ্রাসন বন্ধ করে কৃষি জমি রক্ষায় যে কঠোর ভূমি ব্যবহার নীতির কথা বলা হয়, তার বাস্তবায়ন কোথায়? বাস্তবতা হলো, শক্তিশালী রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং কার্যকর প্রয়োগের অভাবে অনেক ভালো উদ্যোগই কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। আমাদের অবশ্যই ‘ধফধঢ়ঃধঃরড়হ ঃৎধঢ়’ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। চিংড়ি চাষকেও একসময় লবণাক্ত পরিবেশে একটি অর্থনৈতিক অভিযোজন হিসেবে দেখানো হয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটি সংকটকে আরও গভীর করেছে। সুতরাং, যেকোনো সমাধান গ্রহণের পূর্বে তার সম্ভাব্য সামাজিক ও পরিবেশগত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা অপরিহার্য।
উপকূলীয় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আজকের সিদ্ধান্তের উপর। এই সংকট মোকাবেলায় বিচ্ছিন্ন কোনো পদক্ষেপ বা প্রকল্পভিত্তিক সমাধান যথেষ্ট নয়। একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এখন সময়ের দাবি। চিংড়ি চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা না গেলেও, এটিকে অবশ্যই একটি টেকসই ব্যবস্থাপনার অধীনে আনতে হবে। এজন্য সমন্বিত ভূমি ও পানি ব্যবহার নীতি প্রণয়ন এবং কঠোরভাবে প্রয়োগ করা জরুরি। কঠোর জোনিং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষিজমি, মিঠা পানির উৎস ও জলাভূমি রক্ষা করতে হবে এবং কোনোভাবেই উর্বর ধানক্ষেতকে লবণাক্ত পানির ঘেরে রূপান্তর করতে দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি জলবায়ু-সহনশীল কৃষির সম্প্রসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লবণ-সহনশীল ফসলের জাত, সরজন পদ্ধতি এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মতো প্রমাণিত প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে শক্তিশালী কৃষি সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে। এর জন্য সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণও প্রয়োজন।
এছাড়া, যেকোনো উন্নয়নমূলক বা অভিযোজন প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের উপর। তাই কমিউনিটি-নেতৃত্বাধীন অভিযোজন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অর্থায়ন বাড়াতে হবে, যাতে সমাধানগুলো স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং মানুষের মালিকানা নিশ্চিত করে। উপকূলের মানুষকে কেবল ত্রাণগ্রহীতা হিসেবে নয়, বরং জলবায়ু যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। সর্বশেষে, উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য একটি বিশেষায়িত জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি, যার মূল লক্ষ্য হবে শিশু ও মাতৃ-অপুষ্টি মোকাবেলা করা। নিরাপদ খাবার পানির সরবরাহ নিশ্চিত করাও এই কর্মসূচির একটি অপরিহার্য অংশ হতে হবে।
দিনশেষে, উপকূল যদি ভালো না থাকে, তবে বাংলাদেশ ভালো থাকবে না। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার অর্জন অর্থহীন হয়ে যাবে যদি দেশের একটি বিশাল অংশের মানুষ অভুক্ত বা অপুষ্টিতে ভোগে। এই সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের নীতিনির্ধারকদের কাছে এটাই প্রশ্ন— উপকূলের লবণাক্ত পানিতে ভেসে যাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের হাহাকার কি তাদের কর্ণকুহরে পৌঁছাচ্ছে? নাকি তাদের ভাবনা এখনও জাতীয় গড় পরিসংখ্যানের বৃত্তেই সীমাবদ্ধ?
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের কাছে ঘূর্ণিঝড় কেবল একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, প্রতিবছর আঘাত হানা এক আজন্ম অভিশাপ। বিশেষ করে, বছরের বর্ষা মৌসুমের আগে এবং পরে আকাশে মেঘ দেখলেই তাদের মনে দানা বাঁধে এক চেনা ভয়, এই বুঝি হারালাম সবকিছু।
এই ভয়ের একটি ভৌগোলিক এবং বৈশ্বিক কারণও রয়েছে। পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূখ- প্রাকৃতিকভাবেই নিচু এবং সমতল। অসংখ্য নদী-নালা জালের মতো ছড়িয়ে থাকায় এই অঞ্চল যেমন উর্বর, তেমনই অরক্ষিত। বঙ্গোপসাগরের ফানেল আকৃতির উপকূলরেখা সামুদ্রিক ঝড়কে দানবীয় শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেয়। এর সাথে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন নামক বৈশ্বিক অভিশাপ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘূর্ণিঝড়গুলোকে আরও শক্তিশালী ও ঘন ঘন আঘাত হানার পরিবেশ তৈরি করছে। ফলে, যা ছিল প্রকৃতির এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তা এখন এক বিধ্বংসী ও নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। উপকূলের সাধারণ মানুষ, যারা এই জলবায়ু পরিবর্তনে সামান্যতম ভূমিকাও রাখেনি, তারাই এর সবচেয়ে নিষ্ঠুর শিকার।
তবে প্রকৃতির এই রুদ্র রূপের বিপরীতে উপকূলকে মায়ের মতো আগলে রেখেছে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন- সুন্দরবন। সিডর, আইলা বা বুলবুলের মতো প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের সামনে সুন্দরবনই যেন হয়ে উঠেছিল এক প্রাকৃতিক বর্ম। এর অসংখ্য গাছপালা, শ্বাসমূল আর নদ-নদীর ঘন নেটওয়ার্ক ঝড়ের গতিকে অনেকাংশে কমিয়ে দেয়, জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা শোষণ করে নেয় এবং উপকূলের মূল ভূখ-কে সরাসরি আঘাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন, নদীর প্রবাহ কমে যাওয়ায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি, দূষণ এবং বনখেকোদের আগ্রাসনে সুন্দরবন নিজেই আজ বিপন্ন। এই প্রাকৃতিক রক্ষাকবচকে রক্ষা করতে না পারলে ভবিষ্যতে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত বাংলাদেশের জন্য আরও কত ভয়াবহ হবে, তা কল্পনাও করা যায় না। সুন্দরবনকে বাঁচানো তাই কেবল একটি পরিবেশগত বিষয় নয়, এটি উপকূলের কোটি মানুষের জীবন বাঁচানোর সমার্থক।
উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ প্রতিবছর হারায় তাদের স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবা, নিকটাত্মীয়, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি। সিডর, আইলা, ফণী, আম্ফানÑ এসব নামের সাথে মিশে আছে হাজারো মানুষের কান্না আর হারানোর বেদনা। তবে এই দুর্যোগগুলোই তাদের আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তিও জোগায়। এই হারানোর যন্ত্রণা কেবল বস্তুগত বা শারীরিক নয়, এর একটি গভীর মানসিক প্রভাবও রয়েছে। প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়ের পর উপকূলের শিশুদের চোখে যে আতঙ্ক জমা হয়, তা ভোলার নয়। ঝড়ের রাতে বাতাসের হুংকার আর জলোচ্ছ্বাসের গর্জন তাদের শিশু মনে যে স্থায়ী ক্ষত তৈরি করে, তা সারাজীবনেও শুকায় না। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে তৈরি হয় এক ধরনের উদ্বেগ। বারবার ঘরবাড়ি ও জীবিকা হারিয়ে তারা একসময় মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি প্রায়শই ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়।
এই সংকটের সবচেয়ে নীরব শিকার হয় নারী ও শিশুরা। দুর্যোগের সময় এবং পরে তাদের দুর্ভোগ পৌঁছায় চরমে। আশ্রয়কেন্দ্রে অপরিসর ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নারীরা তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত থাকেন। বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশনের অভাবে তারা নানা রকম স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েন, বিশেষ করে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্যোগ পরবর্তী সময়েও সংসারের হাল ধরতে নারীদেরই সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। অন্যদিকে, দীর্ঘ সময় ধরে স্কুল বন্ধ থাকায় শিশুদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয়, যা তাদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়। দুর্যোগের এই লিঙ্গভিত্তিক এবং বয়স-ভিত্তিক প্রভাবগুলো আমলে না নিলে কোনো পুনর্বাসন কার্যক্রমই পুরোপুরি সফল হতে পারে না।
এখানে ঘূর্ণিঝড় বৃষ্টি ও বাতাসের সাথে সাথে নিয়ে আসে লোনা পানির বিশাল ঢেউ আর জলোচ্ছ্বাস। মানুষ কেবল তার শেষ আশ্রয় হারায় না, খাদ্য-বস্ত্র-পানির অভাব তখন সবচেয়ে প্রকট হয়। বাঁধ ভেঙে নদীর লোনা পানি উপকূলে ঢুকে পুকুর, টিউবওয়েলসহ অন্যান্য পানির উৎস নষ্ট করে দেয়। দীর্ঘমেয়াদে ডেকে আনে খাদ্য সংকট এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি। সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায় লবণাক্ততা আর তীব্র বাতাসের তোড়ে। জেলে হারায় তার মাছধরার জাল ও নৌকা। অনেকেই হারায় তাদের জীবিকার অনুসঙ্গ, যার ফলে বেড়ে যায় অপরাধপ্রবণতা। লোনা পানির এই আগ্রাসন কেবল তাৎক্ষণিক সংকট তৈরি করে না, এটি উপকূলের কৃষি অর্থনীতি এবং বাস্তুতন্ত্রকে স্থায়ীভাবে বদলে দেয়। যে জমিতে একসময় সোনার ধান ফলত, লবণাক্ততার কারণে তা আজ বন্ধ্যা। বাধ্য হয়ে অনেক কৃষক তাদের শতবর্ষের পেশা ছেড়ে চিংড়ি চাষ বা অন্য পেশায় ঝুঁকছে। চিংড়ি চাষ লাভজনক হলেও এটি মাটির উর্বরতা আরও কমিয়ে দেয় এবং লবণাক্ততা বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে মিষ্টি পানির মাছ ও দেশীয় প্রজাতির উদ্ভিদ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এটি একটি চক্রাকার সংকট তৈরি করে। ঘূর্ণিঝড় লবণাক্ততা বাড়ায়, আর সেই লবণাক্ততা কৃষিকে ধ্বংস করে মানুষকে এমন পেশার দিকে ঠেলে দেয়, যা পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি করে। এর ফলে উপকূলের খাদ্য নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ওপর এক নীরব আঘাত নেমে আসে।
বেশিরভাগ মানুষ সঠিক খবর ও সচেতনতার অভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না। যারা আশ্রয় গ্রহণ করে তারা ফিরে এসে বাড়ির খোঁজ নেয়, হারিয়ে যাওয়া গবাদিপশুটির খোঁজ নেয়। ঘূর্ণিঝড় বাড়িঘর আস্ত রাখে না, অনেকসময় মেরে ফেলে তাদের সম্বল গবাদি পশুদের। কিন্তু, এই অদম্য মানুষগুলো আবার ঘুরে দাঁড়ায়। চোখের পানিকে আড়াল করে ঘাম ঝরিয়ে পরিশ্রম করে, গড়ে তোলে আরেকটা বাড়ি, মাছে ভরা পুকুর, গোয়ালভরা গবাদি পশু-পাখি। কিন্তু, এসব আয়োজন যেন আবার ঘূর্ণিঝড়ের কাছে সঁপে দেওয়ার জন্যই।
তবে এই ঘুরে দাঁড়ানো এখন আর কেবল ভাঙা ঘর নতুন করে গড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। প্রকৃতির সাথে লড়াই করতে করতে উপকূলের মানুষ শিখে নিয়েছে অভিযোজনের নিজস্ব কৌশল। তারা এখন অতীতের অর্জিত জ্ঞানের সাথে আধুনিক প্রযুক্তিকে মিলিয়ে টিকে থাকার নতুন পথ খুঁজছে। অনেকেই মাটির ভিটার উচ্চতা বাড়িয়ে ঘর তৈরি করছেন। বর্ষাকালে বাড়ির চারপাশে ভাসমান সবজির বাগান তৈরি করছেন কেউ কেউ, যা জলোচ্ছ্বাসেও নষ্ট হয় না। লবণাক্ততা-সহনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন ও চাষাবাদ বাড়ছে। কমিউনিটি-ভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি দল গঠন করে তারা নিজেরাই নিজেদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছে।
উপকূল রক্ষায় বেড়িবাঁধগুলোই প্রথম প্রতিরোধ ব্যবস্থা। কিন্তু অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ, দুর্নীতি এবং নদী ভাঙনের কারণে অনেক বাঁধই দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ। একটি শক্তিশালী জলোচ্ছ্বাসের ধাক্কা সামলানোর ক্ষমতা তাদের থাকে না। আবার আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। যেগুলো আছে, তার অনেকগুলোই মূল বসতি থেকে দূরে হওয়ায় নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য সেখানে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। দুর্যোগের সময় সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে আশ্রয়কেন্দ্রের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে।
তাছাড়া, যখন একজন কৃষক নদী ভাঙনে তার জমি হারায়, একজন জেলে তার নৌকা হারায় এবং একজন দিনমজুর তার কাজ হারায়, তখন নিজের গ্রামে টিকে থাকার আর কোনো উপায় থাকে না। জীবন ও জীবিকার তাগিদে হাজার হাজার পরিবার প্রতি বছর উপকূল ছেড়ে শহরের দিকে পাড়ি জমায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম বা খুলনার মতো বড় শহরের বস্তিগুলোতে আশ্রয় নেয় তারা, যেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করে এক ভিন্নধর্মী সংগ্রাম। মাটির সঙ্গে বেড়ে ওঠা এই মানুষগুলো শহরের ইট-পাথরের জীবনে খাপ খাওয়াতে পারে না। তারা তাদের পরিচিতি হারায়, সামাজিক বন্ধন হারায় এবং প্রায়শই ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এই জলবায়ু-শরণার্থীদের গল্পগুলো জাতীয় পরিসংখ্যানে প্রায়শই হারিয়ে যায়।
ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের পাশে দাঁড়ায়, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে, এমনকি ঘর মেরামতের ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু, স্থানীয় রাজনীতির চক্করে পড়ে অনেক সময় মূল ক্ষতিগ্রস্তরা এসব সাহায্যের বাইরে থেকে যায়। ত্রাণ কার্যক্রম প্রায়শই তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন, যেমন- টেকসই জীবিকার ব্যবস্থা করা, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, অথবা জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণÑ এসব দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না। ফলে, একটি দুর্যোগের ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই আরেকটি এসে আঘাত হানে, এবং মানুষগুলো এক ত্রাণ-নির্ভরতার দুষ্ট চক্রে আটকা পড়ে যায়।
এখন প্রশ্ন হলো, এই অন্তহীন সংগ্রামের শেষ কোথায়? কেবল ত্রাণ বা তাৎক্ষণিক সাহায্য দিয়ে এই সমস্যার মূল উৎপাটন করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন একটি সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। টেকসই ও মজবুত বেড়িবাঁধ, পর্যাপ্ত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী তৈরি করতে হবে, তেমনই লবণাক্ততা-সহনশীল কৃষি ব্যবস্থা ও বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করতে হবে। আন্তর্জাতিক পরিম-লে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে ‘লস অ্যান্ড ড্যামেজ’ বা ক্ষয়ক্ষতি পূরণের তহবিল আদায়ে সোচ্চার হতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সকল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, তারাই এই সংকটের প্রধান ভুক্তভোগী এবং তারাই জানে টিকে থাকার সেরা উপায়। উপকূলকে বাঁচাতে হলে তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকেও সম্মান জানাতে হবে।
ভারতের বিমাতাসুলভ আচরণের ফসল ফারাক্কার প্রভাবে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনকে ঘিরে রাখা ৫৩ নদী নাব্যতা হারিয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বন্ধুপ্রতীম দু’দেশের পানি চুক্তি আছে, কিন্তু বণ্টন নীতিতে রয়েছে যোজন যোজন ফারাক। ফলে সুন্দরবনের নদ-নদীর জলজ প্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্ব রয়েছে চরম সংকটে। ফারাক্কা ও অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনার অভাবে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার নদীর নাব্যতা আজ বিপন্ন। অপরিকল্পিত জলকপাট ও বাঁধ দেয়া হয়েছে। সুন্দরবনসহ খুলনার যে নদীগুলো নাব্যতা হারিয়েছে, তার প্রধান কারণ ফারাক্কা বলে দাবি করেছে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা। আর নাব্যতা হারানো অধিকাংশ নদীই সুন্দরবন বেষ্টিত খুলনাঞ্চলে।
দেশে মোট নদীর সংখ্যা এক হাজার আটটি। খুলনা বিভাগে নদ-নদীর সংখ্যা ১৩৮টি। দখলদারদের লোভের শিকারে খুলনা বিভাগের ৩৭টি নদীসহ সুন্দরবন সংলগ্ন মোট ৫৩টি নদী সংকটাপন্ন। এরমধ্যে ২৭টি নদী প্রবাহমান নেই, নয়টি নদী আংশিক প্রবাহমান রয়েছে। বাকিগুলো স্রোত না থাকায় ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। এ কান্নার যেন দেখার কেউ নেই।
শিবসা ও কপোতাক্ষ নদীকে বলা হয় সুন্দরবনের অক্সিজেন। এরাই এখন নাব্যতা সংকটে ভুগছে। এছাড়া নাব্যতা সংকটে থাকা খুলনার অন্য নদীগুলো হলো- গড়খালি, নৈর, সৈয়দখালি, হরিণখোলা, হরি, হাড়িয়া, হাবরখালি, নোয়াই, পশুর, পুরাতন পশুর, বাতাঙ্গি, বাদুরগাছা, বানিয়াখালি, বিগরদানা, ভদ্রা, মঙ্গা, মধুখালি, ময়ূর, মরা ভদ্রা, মিনহাজ, মির্জাপুর, রাধানগর, লতা, পুতলাখালি, গাছুয়া, গুনাখালি, গেউবুনিয়া, গোয়াচাবা, ঘোষখালি, ঘ্যাংরাই, চাঁদখালি, চিত্রা, চুনকুড়ি, জিরবুনিয়া, ঝপঝপিয়া, ঢাকি, তালতলা, তেলিখালি, দিঘলিয়া, দেলু, শাকবাড়িয়া, শামুকপোতা, শোলমারি, সালতা, উত্তর কাঠামারি, কয়রা, নালুয়া, কাটাবুনিয়া, কালিনগর, কিচিমিচি, কুরুলিয়া, জিলে ও চকরিবকরি।
সুন্দরবন হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের রক্ষা কবচ। টর্নেডো, ঘুর্ণিঝড় কিংবা সাইক্লোনের ছোবল থেকে এই সুন্দরবন বুক পেতে দিয়ে আগলে রাখে গোটা অঞ্চলকে। উপকূলের কোটি-কোটি মানুষকে নিরাপদ রাখতে ও তাদের জীবিকা নির্বাহে সুন্দরবনের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। অথচ বছরের পর বছর সেই সুন্দরবনই ভালো নেই। নদীগুলো অপশাসনের কারণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ নদী-খালগুলো ভরাট হয়ে যেতে শুরু করেছে। পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাওয়া এ সকল নদী ও খালে জোয়ারের পানি ঢুকছে না, ভাটার সময় পানি নামছে না। ফলে বনের ভেতরে লবনাক্ততা বেড়েই চলেছে। যা সুন্দরবনের প্রাণী ও জীববৈচিত্রের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। মাঝে মধ্যেই সুন্দরবনের হরিণ, বাঘসহ বিভিন্ন প্রাণী খাদ্য ও পানির জন্য লোকালয়ে প্রবেশ করছে। ইদানিং এ সংখ্যা বেড়ে গেছে।
ভারতের আগ্রাসী বৈদেশিক নীতির ফলশ্রুতিতে ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে খুলনা অঞ্চলের নদীগুলোর প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলে মনে করেন পানি বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার লুৎফর রহমান। তিনি বলেন, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীতে পানি আসে গঙ্গা অববাহিকা থেকে। ফারাক্কায় যে শুভংকরের ফাঁকির স্রোত বহমান সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগন্য। সময় মতো তাই এ অঞ্চলের নদ-নদীগুলো পানি পায়না। যা এ অঞ্চলের নদ-নদীগুলোর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তাছাড়া উজান থেকে যে পানি আসে, সেটা গড়াই দিয়ে ঢোকে। সেই গড়াইয়ের মুখেও প্রতিবন্ধকতা আছে। দু’দেশের মধ্যে পানির হিস্যা নিয়ে যে বন্টকনামা রয়েছে তার বাস্তবে কোন প্রয়োগ নেই। ফলে নদ-নদীগুলো অসুস্থ হয়ে পড়ছে দিনের পর দিন।
আরেক নদী গবেষক মাহবুব সিদ্দিকীও ফারাক্কাকে দায়ী করেছেন। ইনকিলাবকে তিনি বলেন, গঙ্গাই হচ্ছে খুলনাঞ্চলের নদীগুলোর পানির উৎস্য। পদ্মা থেকে পানি নিয়ে মাথাভাঙ্গা, শিয়ালমারি, হিসনা, গড়াই, চন্দনা ও ভৈরব নদ-নদী প্রবাহিত হয়। পদ্মায় যদি স্রোত থাকে তাহলে সেখান থেকে পানি গড়িয়ে এ নদীগুলোতে যায়। পরে সেটি বিভিন্ন নদী হয়ে সুন্দরবনাঞ্চলের নদীগুলোতে মেশে। বর্তমানে পদ্মাতেই পানি কম। ফারাক্কার কারণে পদ্মাসহ এসকল নদ নদী নাব্য হারাবে, সেটাই স্বাভাবিক।
অপরদিকে, খুলনা জেলা সদর থেকে খোদ দক্ষিণে আগে নদীপথে পণ্য পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল। নাব্য সংকটে সেটি আর নেই। এছাড়া নদী নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী যারা ছিল, তারা পেশা হারিয়েছে। পাশাপাশি নদীগুলো মাছের প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল, যা এখন আর নেই। আবার মাছের ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন প্রাণী যেমন পাখি, ভোদড়, শুশুক কমে গেছে। অথচ ২৪ ঘণ্টায় ছয় বার প্রাকৃতিক রূপ বদলানো সুন্দরবনের মোট আয়তনের ৫২ ভাগই এখন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অংশ। তাছাড়া মৎস্য প্রজনন ও অভয়ারণ্য বলে খ্যাত ভদ্রায় এখন মাছের প্রজনন রীতিমতো শুন্যের কোঠায়।